ঘটনাবহুল রবীন্দ্রনাথ
- May 9, 2021
- 4 min read
ডঃ অতসী সরকার

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ এবং তিরোধান ১৯৪১ মোট ৮০ বৎসর- জীবিতকালে তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য অমূল্য সম্পদ তাঁর সৃষ্টি-ভারতবর্ষের জন্য নোবেল পুরস্কার, শান্তিনিকেতন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য মিলন নিকেতন। তাই আজও শুধু স্বদেশ নয় সেই সময় থেকে বহির্দেশেরও বহু জ্ঞানীগুণি মানুষের আশ্রয়স্থল হিসাবে আজও চিহ্নিত।রবীন্দ্রনাথের সেই ঘটনা বহুল জীবন ও কর্ম পরিধির পর্যালোচনা করলে তার একটা উত্তর পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ সার্বভৌম কবি।বহু মনু কবি, শিল্পী তাঁর সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছেন। আমরা যেমন পশ্চিমবঙ্গ বাসীরা তাঁর জন্মস্থান জোঁড়াসাকোকে নিয়ে গর্ব করি, তেমনি ওপার বাংলার মানুষেরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তারা গর্ব করেন, এমন কি তাঁর রচিত “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটি তাঁদের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে তাঁরা নির্বাচিত করে কবিকে সাদরে বরণ করেছেন। যা দুই উপ-মহাদেশকে নিবিড়ভাবে একই ফুলহারে বেঁধে রাখতে সমর্থ হয়েছে৷ রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় ব্যক্তি-চেতনার দ্যুতিতে স্বয়ংসিদ্ধ যাঁর জীবনে ছিল নূতন সহজ ও স্বছন্দ গতিতে সমাজ গড়ে তোলা। তাঁর কীর্তি যশ খ্যাতি গগনচুম্বি। তিনি আপন ঐশ্চর্য্যেই চিরকাল অম্লান আলোকে বিকশিত থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্য চেতনা কি ভাবে জন্মাল তা বিস্ময়কর ব্যাপার-তবে বাল্যরচনার মধ্য দিয়ে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা শুরু থেকেই ছিল সর্বতোমুখী। কাব্যে,গানে,নাটকে,উপন্যাস-সাহিত্যের সমগ্র ভুবনে তিনি একাই সমৃদ্ধ, সমুজ্বল করে গেছেন। তাঁর সাহিত্য রচনা মাত্র তের/চোন্দ বছর বয়স থেকে শুরু হয় এবং তখন থেকেই তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে থাকে। চোদ্দ থেকে আঠারো বছর বয়সের মধ্যেই তিনি লেখেন ‘কবি কাহিনী’, ‘বনফুল’, ‘ভগ্নহদয়’, ‘কাল মৃগয়া’, ‘শৈশব সঙ্গীত’ (১৮৮৪) বিবিধ।
রবীন্দ্র কাব্যের বিশাল পথ পরিক্রমায় প্রথম দিকের রচনাগুলি বাদ দিলে ইতিহাসের নিরিখে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। যেমন-
প্রথম অধ্যায় কৰি প্রকৃতি ও প্রেমের পূজারী।সন্ধ্যা সংগীত, প্রভাত সঙ্গীত,ছবি ও গান,কড়ি ও কোমল, মানসী ও সোনারতরী (১৮৯৩)।
দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর জীবন দেবতাকে উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থগুলি হল–চিত্রা, চৈতালি, নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলি (১৯১০)
তৃতীয় অধ্যায়ে -এ অধ্যায়ে কবি ছবি এঁকেছেন প্রাণ চঞ্চল পৃথিবীর। কাবগ্রন্থগুলি হল-বলাকা, পূরবী ও মহুয়া (১৯২৯)।
চতর্থ অধ্যায়টি অতীব বেদনার,বিচিত্র ব্যথা-বেদনা তাঁর অন্তরকে নাড়া দিয়েছে-কাবগ্রন্থগুলি হল-
প্রান্তিক,নবজাতক,আরোগ্য,জন্মদিনে,রোগশয্যায় (১৯৪১)
রবীন্দ্র কাব্য-ভুবনের বিশালতা ও বৈচিত্রের সবটুকু তাঁর একক সৃষ্টি। তাঁর গানে-কবিতায় যেমন বাঙালী বৈষ্ণব বাউলদের ছায়া আছে, রবীন্দ্র ভাবনায় সুফিবাদের প্রভাবও আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করি-তেমনি তাঁর কবিতার মধ্যে শেলী,কিটস, ওয়ার্ডসওয়াখ-এর মত প্রকৃতিপ্রেমকেও লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন, কবি ধর্ম অসামান্য স্বকীয়তায় অধিষ্ঠিত সেখানে তিনি সৃষ্টিকর্তার মতো স্বয়ংসম্পুর্ণ। তাঁর নষ্টনীড় এবং চোখের বালি বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস-এই দুইটি দীর্ঘ কাহিনী নির্ভর উপন্যাস-এই দুইটি উপন্যাস নিয়ে নাটক হয়েছে, সিনেমা হয়েছে যা দেখে দর্শকরা কখনো ক্লান্তি অনুভব করে নি। এরপর নৌকাডুবি, গোরা এক বিস্ময়কর সার্থক এই উপন্যাসের মধ্যে বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘গোরা’। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এই ‘গোরা’কে অবলম্বন করে যখন সিনেমা হয় তার মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহসিক্ত অনুজ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বিশ্বভারতীর আপত্তি থাকলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীতগুলি এ ফিল্মে স্থান পাওয়ার জন্য ছাড়পত্র দেন।
প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ গল্প রচনা দিয়ে শুরু করলেও রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে যে দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন তা বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর দায়িত্ব নিয়ে ত্রিশ বছর বয়সে বাঙলার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। বাঙলার পল্লী জীবন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদী নালা, গাছপালা, উন্মুক্ত প্রান্তর, নীলাকাশ তাঁকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করেছে৷ পল্লীবাসীর সুখ,দুঃখের কাহিনী-সাম্প্রদায়িকতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে হিন্দু-মুসলিম-খ্রীস্টান–শিখ-জৈনকে এক জাতি-এক প্রাণ হিসাবে তাঁর কাব্যে-সাহিত্যে-নাটকে মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প সংখ্যা প্রচুর, বৈচিত্রে অ-সাধারণ। বাঙলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথই ছোট গল্পের সৃষ্টিকর্তা ও প্রবর্তক।
১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গের ফলে তৎকালীন বঙ্গদেশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই-১) পূর্ববঙ্গ ২)পশ্চিমবঙ্গ।১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান।১৯৭১ সালে পুনরায় হয় “বাঙলাদেশ”। বাঙালীদের বুকে চেপে থাকা পাথর নেমে যায়। বাঙালী ফেলতে পারলো নিঃশ্বাস। বাঙলা ভাষা পেল রাষ্ট্রীয় মর্যাদা-এই পূর্ববঙ্গবাসীদের জোরালো দাবী। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কবি-তিনি হিন্দুও নন তিনি মুসলমানও নন, তিনি ব্রাহ্ম নন, তিন অমৃতের সন্তান-একজন মানুষ। একটি আনন্দময় সত্তা, শাশ্বত কবি। জাতপাত জাতিভেদ তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। তিনি অনন্ত অসীম ও সনাতন। তাই দুই দেশের কবি সাহিত্যিকরা বলেন, রবীন্দ্রনাথ নজরুল যেমন আমাদের কবি তেমনি বঙ্গ সংস্কৃতি, বাঙলাভাষা আমাদের, এই সংস্কৃতি আমাদের কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।
১৮৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের গান দিযে শুরু হয়-
‘আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা?।‘
ঢাকা থেকে ফিরে কবি শিলাইদহে গমন করেন। এখন শিলাইদহ বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় অন্তর্গত। এই শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের জমিদারীর একটা অংশ ছিল।সেখানে ছিল রবীন্দ্রনাথের কুঠীবাড়ী।
তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারী প্রথার আমূল সংস্কার এবং এখান থেবেই পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ঢাকা শহরে দুটি কলেজ মাত্র। একটি ঢাকা কলেজ অন্যটি জগন্নাথ কলেজ। এরপর দুইটি কলেজের নাম হয় ইন্টারমিডিয়েট কলেজ।এই জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন অনেকদিন পূর্বে যখন তোমরা অনেকেই জন্মগ্রহণ করনি তখন আমি একবার বলেছি যে আমাদের দেশের সভ্যতা আত্মীয়তামূলক সভ্যতা। আমি নিজে কলকাতায় জন্মেছি-সেখানে দেখেছি আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল, সেখানে মিলমিশ শুধু মাত্র সভা সমিতিতে, হৃদয়ের যোগাযোগ সেখানে নেই।আমি শহরে থাকি কিন্তু সে যেন একটা কারখানা-সেখানে প্র্যোজনের জন্য আত্মীয়তা হতে পারে-কিন্তু আত্মীয়তার শান্তি স্থাপনের জন্য সর্বত্র জলাশয় জেগে উঠবে, ভাঙা দেউল গড়ে উঠবে-অবতার সমস্ত দেশ মুখরিত হয়ে উঠবে আনন্দে-কল্যাণে-সখ্যে।
যেদিন আবার গ্রামের প্রাণ জাগবে সেদিন হিন্দু মুসলমান উভয়ে সমান ভোগ করবে, তখন দরদ হবে, আনন্দ নিকেতনে উভয়ের অমৃত পাতে পড়বে।যেদিন প্রাচুর্য হবে সেদিন বিরোধ ঘুচে যাবে।ভাইয়ে ভাইয়ে ভিন্ন হতে দেখেছি কিন্তু পুজোর দিন আবার মিল হয়। সেদিন বিরোধ থাকে না।সেদিন ঘরে অভাব থাকে না। অন্নের জন্য মারামারি থাকে না, কিন্তু দানের জন্য ব্যগ্রতা থাকে।ঘুষ দিয়ে আত্মীয়তা হয় কেবলমাত্র পুলিস কিংবা দস্যুর সঙ্গে।
১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথঠাকুরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধি প্রদান করা হয়।শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি সেই সময় যেতে পারেন নি।কিন্তু এই ঘটনার আগে ও পরে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছেন। কুমিল্লায় ৬ দিনব্যাপী কবিগুরুর সার্ধশতজন্মবার্ষিকী উদযাপন হয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা মনে রাখার মতো। এই সভায় ভাইস চ্যান্সেলার ল্যাংলী সভাপতিত্ব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, জীবনের পরিণতি মৃত্যু। জীবনের হতাশাব্যঞ্জক দুঃখজনক ঘটনা এক হিসাবে তখনই সুন্দর হতে পারে না। কিছু এটাই যখন শিল্পের চিত্রের পটভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে -তখন এটা বাস্তবরূপে আমাদের আনন্দ দেয়, এতে প্রমাণ হয় যে -প্রত্যেক বস্তু যা আমাদের মনের কাছে তার অস্তিত্বের দাবী রাখে তা সুন্দর। সংস্কৃতে একে বলা হয় মনোহর অর্থাৎ মনের হরণকারী। বিজ্ঞানের রাজ্যে যেমন অঙ্ক তেমনি সকল শিল্পের নিষ্কাশন হচ্ছে সঙ্গীত।যারা সত্যিকার বড় ও অকপট তাঁদের মহত্বের একটা চিহ্ন এই যে অপরের কাছ থেকে আহরণের ক্ষমতা তাদের অত্যন্ত বেশী এবং তারা প্রায়ই তাদের অজান্তে বিশ্বের সভ্যতার বাজারে সীমাহীন ঋণ করে বসেন। মাঝামাঝি সম্পন্ন ব্যাক্তিরাই কেবল এই আহরণে লজ্জিত ও ভীত হয়। আমাদের ভাগ্য ভাল যে-এই দেশে ইউরোপীয়দের আসার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে বাংলা সাহিত্য এসেছিল। তার ফলে আমাদের মনের বহুল পরিবর্তন হয়েছে সত্য-কিন্তু একথাও সত্য যে ভারতআত্মাকে বাঁচিয়ে রেখে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা অধিকতর সমৃদ্ধশালী হয়েছি। ঈশ্বর তাঁর নিজের সৃষ্টির মধ্যে বাস করেন - মানুষের কাছেও ওটা আশা করা যায় যে-সেও তার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। শিল্পাদর্শ নিছক বিলাস বা কল্পনা নয়, তা চরম বাস্তবভিত্তিক।
“আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়াছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে। (বাঁশি)

লেখিকা পরিচিতি
ডঃ অতসী সরকার, রবীন্দ্রমেলার সদস্যা।

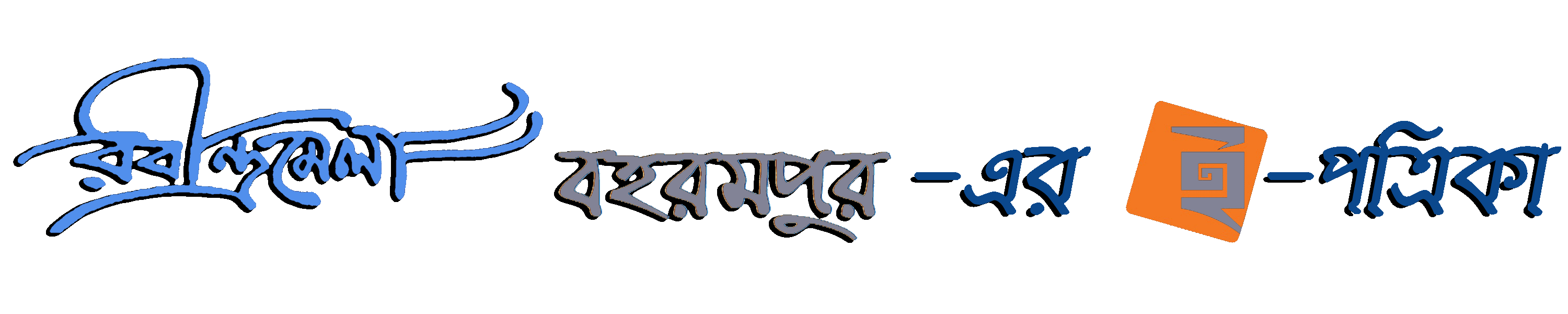
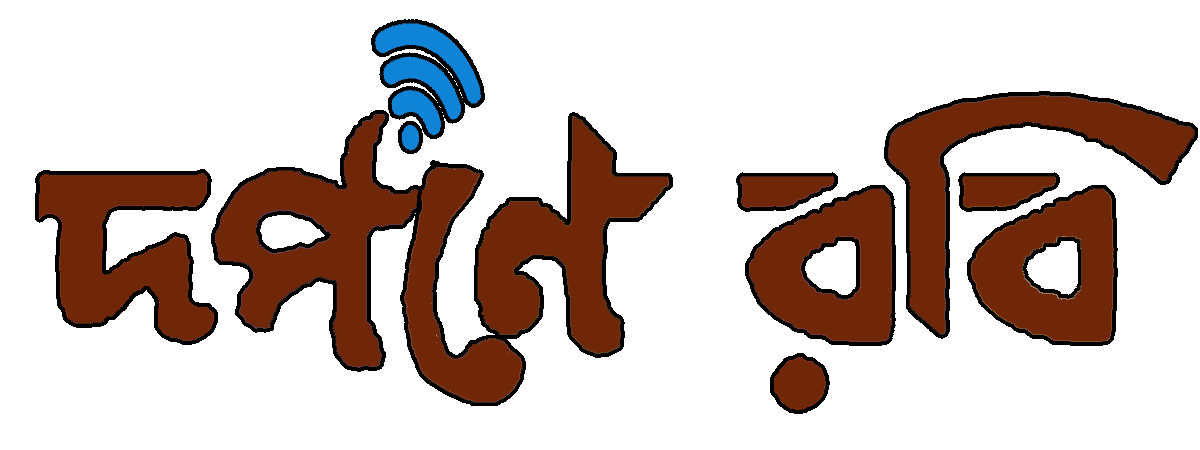







Comments