রবীন্দ্রনাথের গল্পঃ বিষয় রাজনীতি
- Aug 8, 2021
- 5 min read
ক্ষেত্র গুপ্ত

প্রাজ্ঞ সমালোচকরা অনেকে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে স্থূল বস্তুভার নেই, প্রায়ই তা লিরিক নির্যাস, তাতে নিখিলের নিঃশ্বাস; আর সেখানেই তার মহিমা। এবং তিনি নাকি প্রকৃতির আড়াল থেকে মানব সংসারকে দেখেছেন পদ্মায় বোটে যেতে যেতে, তাই বর্ণাঢ্য ইন্দ্রধনুতে কল্পনার মাত্রা অবাধ হতে পেরেছে।
গল্পগুলি নিজেরা কিন্তু অন্য সাক্ষ্য দেয়। কখনও কোথাও গীতিকবিতার কোনো নির্বস্তুক সুর থাকলেও, এই লেখাগুলি বড় বেশি জীবনের সত্যকে প্রকাশ করে। সমাজে সময়ে বুনট একান্ত বাস্তব সমস্যার বৈচিত্র বহুলতায় এত খাঁটি বিচরণ, এত গভীর কমিটমেন্ট এবং গাঢ় শিল্পবন্ধ উত্তরাধিকারের কাছে রইল দুর্লভ প্রাপ্তি হয়ে।
অবশ্য ‘লিপিকা’র কয়েকটি লেখায় গল্পে কবিতার মিশেল দিয়ে নতুন শিল্প সত্যের খোঁজ মিলেছে। সে’র রচনাগুলিতে ফ্যান্টাসি-ননসেন্স-অ্যাবসার্ডের গভীরে আপাত বাস্তবতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অন্যতর বাস্তবের আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে। কতকটা ‘গল্পেসল্পে’ও। কিন্তু গল্পের মূল ধারা সরাসরি বস্তুবিদ্ধ জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ানোয় তাতে ডোবা-ভাসা এবং তলিয়ে যাওয়ায়;- তাই ‘গল্পগুচ্ছ’ ধারার ঘটনায়-মানুষের জড়ানো কাহিনী অবিরাম চলেছে। ‘সে’-র পরেও এসেছে ‘তিনসঙ্গী’; ‘গল্পসল্পে’র পাশে পাশে লেখা হয়েছে ‘প্রগতিসংহার’, ‘মুসলমানীর গল্প’।
পঞ্চাশ বছর ধরে গল্প লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৪৮।‘গল্পগুচ্ছ’, ‘তিনসঙ্গী’ তে ৯৬টি, লিপিকা (শুধু গল্প জাতীয় লেখা) সে, গল্পস্বল্প মিলে আরও ৫২টি- অনেক গল্প। রীতি-স্বাদ যাইহোক, পরীক্ষার যেকোনো ভঙ্গিতে জগতকে দেখতে চান না উল্টেপাল্টে, গল্পের শিকড় ছড়ানো জীবনের মধ্যে সর্বদাই সমান গভীর যদি না-ও হয়।
-দুই-
ওই কালসীমায় অনেক রকম মানুষ, বলব না সবরকম-এবং অনেক সমস্যা ভিড় করে আছে-এক অতি বিস্তৃত মানব পৃথিবী। সোৎসাহে বলা যায় ‘হিয়া্র ইজ গডস্ প্লেনটি’। লেখক স্বয়ং বলেছেন তাঁর গল্পে আছে ‘ছোট প্রাণ ছোট কথা’ নিতান্তই সহজ-সরল’ কাহিনী। তার সঙ্গে মিলেমিশে অসামান্য-জটিল-গভীর-ভাঙ্গাবাঁকা জীবন। অন্য সবকিছুর মতোই বিষয় হিসেবে রাজনীতি এসেছে অনেক গল্পে- কোথাও মূলত, কোথাও প্রাসঙ্গিকভাবে। যেমন একরাত্রি, মেঘ-রৌদ্র, দুরাশা, রাজটীকা, নামঞ্জুর গল্প, সংস্কার, বদনাম, শেষকথ্ বিদূষক, ধ্বংস, সামান্যত, স্ত্রীর পত্র এবং নষ্টনীড়।
মোট গল্পের হিসেবে অনুপাতটা বেশি নয়। কিন্তু সেকালে জীবনে সমাজে রাজনীতি যতটা ঢুকে পড়েছিল তার সঙ্গে সমানুপাত রক্ষিত। একালের মত তখনও যদি রাজনীতি এমন সর্বগ্রাসী
হত এ জাতীয় গল্পের সংখ্যা বেড়ে যেত, এমন অনুমানের কারণ আছে।
সাধারণভাবে কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করার মত।
১)কখনও কোন গল্পে রাজনীতির ব্যাপার এত হঠাৎ এসেছে যে অবাক হতে হয়, অথচ এত তাৎপর্যপূর্ণ তার প্রয়োগ যাতে অপরিহার্য মনে হয়। যেমন নষ্টনীড়ের সমস্যা রাজনৈতিক নয়। কিন্তু সংবাদপত্রে নিবেদিত চিত্ত ভূপতির ভাবনাযর জগত স্পষ্ট ও সত্য হয়ে ওঠে সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ উল্লেখে। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের প্রতি কটাক্ষটি তীব্র-
ভারত গবর্নমেন্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত হইয়া সংযমের বন্ধন বিদীর্ণ করিবার দিকে যাইতেছে, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষ্যের বিষয় ছিল।
এই রাজনৈতিক মন্তব্য সম্পাদক ভূপতিকে একজন মডারেট লিবারেলপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আবার ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পের নায়িকা মৃণালের ভাইয়ের বিপ্লবী চরিত্র গল্পের মূল সামাজিক সমস্যাটির সঙ্গে একটা অতিরিক্ত রাজনৈতিক মাত্রা যুক্ত করেছে। ইংরেজবিরোধী শরৎ অনায়াসে নারীর লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে বাড়ির কর্তারা কত সহজে চূড়ান্ত সামাজিক রক্ষণশীলতা এবং সাহেব তোষণকে একসূত্রে বেঁধেছে। নেহাৎ প্রসঙ্গক্রমে এ অংশ গল্পে এসেছে, কিন্তু লেখকের রাজনৈতিক সামাজিক চেতনা কত সুসঙ্গত তার নিদর্শন হয়ে থেকেছে।
২) ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন গল্পে সময়ের গতি রাজনৈতিক ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। ১৮৯২ সালের ‘একরাত্রি’ গল্পের নায়ক ম্যাটসনি-গ্যারিবল্ডির আদর্শে স্বদেশসেবা করতে চেয়েছিল, ১৯৪০-৪১ সালের ‘ধ্বংস’ (গল্পস্বল্পের অন্তর্ভুক্ত) গল্পে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সংক্ষেপে চিত্রিত এবং বিশ্বশান্তির ব্যাকুলতা সংহত হয়ে আছে। ১৯২৬ সালে ‘সংস্কার’ গল্পে অসহযোগ, বিদেশী বয়কট, হরিজন-মুক্তির বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। ১৯৪১-এ মুদ্রিত গল্পে যে বিপ্লবীর কথা বাংলার সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্যে তার উত্তরাধিকার। ত্রিশের দশকের বীর যোদ্ধাদের স্মৃতি এ গল্পে উচ্চারিত এমন অনুমান সংগত।
৩) ‘লিপিকা’য় একটি গল্প আছে ‘বিদূষক’- পুরনো কালে স্থাপিত; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুঢ় চেহারা ছাড়া কোথাও অতীতের রঙের ঢাকা নয়। লেখকের উচ্চ ভর্ৎসনা বিদূষকের মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছে।
বিদূষক বললে, ‘আমি মরতেও পারি নে, কাটতেও পারি নে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব’। সাম্রাজ্যের লোভে রাজা হাসিকে হত্যা করেছে, ম্যাকবেথ যেমন খুন করে ছিল ঘুমকে।
৪) ‘দুরাশা’ ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্সধর্মী গল্প হলেও এর বিষয়টা আসলে রাজনৈতিক। কারণ সিপাহী যুদ্ধের কথা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে। তা শুধু ঐতিহাসিক নয়, গত রাজনীতি-মনস্কতার দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যবহ। সাতান্নর মহাবিদ্রোহ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এই কাহিনীতে। নবযুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এই সংগ্রামের গৌরব স্বীকার করেন নি। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৮৯৮ সালে লেখা এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ উপাদান হিসেবে একে গ্রহণ করেছেন, তিরস্কার করেন নি, বরং নানা ভাবে এর মহিমা প্রকাশ করেছেন।
কেশরলাল বলিল, ‘এইবার গোখাদক গোরালোককে আর্যাবর্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর একবার হিন্দুস্তানে হিন্দু-মুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বসাইতে হইবে।’
যখন হিন্দুস্থানে সমস্ত হিন্দু মুসলমানদের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়ছে তখন তার মধ্য থেকে কেশরলালের যে ব্যক্তিচরিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে তাতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই স্বাধীনতা যুদ্ধ একটি গৌরবের ভূমিকায় দীপ্ত। সমকালীন বুদ্ধিজীবী বাঙালির তুলনায় রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রতিফলিত এই ইতিহাস চেতনা অনেক বেশি ক্রান্তিদর্শী।
-তিন-
আপোষহীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রবীন্দ্রনাথের গল্পের কংগ্রেস সম্পর্কে মনোভাব কখনোই খুব একটা অনুকূল ছিল না, তা ১৮৯৮ বা ১৯২৬ যখনই লেখা হোক না কেন। ১৮৯৮-এ লেখা ‘রাজটীকা’ একটি রাজনৈতিক ব্যঙ্গ। তখন পর্যন্ত ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তেমন তীব্র হয় নি, সংগঠনও ছিল শিথিল ধরণের।কংগ্রেস তখনও ইংরেজিয়ানা ছাড়েনি। রবীন্দ্রনাথের পরিবারেও ব্যক্তিগতভাবে স্বদেশীভাব এত খাঁটি ছিল যে সমকালীন কংগ্রেসকে তীব্রভাবে করতে তিনি ভোলেন নি। যেমন-
কংগ্রেস সভায় যখন পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজাতীয় বিলাতি ‘হিপ হিপ হুররে’ শব্দে তাঁহাকে উৎকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।
কিন্তু যত দুর্বলতাই কংগ্রেসের থাক, সরকারী তাবেদারী এবং কংগ্রেসী কুন্ঠিত জাতীয়তাবাদের মধ্যে বেছে নিতে লেখকের ভুল হয়নি। তিনি খয়ের খাঁ শ্রেণীকে নির্মমভাবে কশাহত করেছেন এ গল্পে। রবীন্দ্র ব্যঙ্গে এত ধার খুব বেশি দেখা যায় না। লেখক সরাসরি যখন কিছু বিবৃত করেছেন তখন ভর্ৎসনা একটুও আবরণ রাখে নি। রচনার সর্বত্র ভাষার ঝকঝকে দাঁত দেখা যাচ্ছে
‘সংস্কার’ গল্পে বিলেতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করা স্বদেশীওয়ালাদের আঁতের ব্যাধি টেনে বের করেছিলেন। ওদের সৌখিন, হুজুগে হাততালি হাততালি-কুড়ানো আন্দোলনে তাঁর মন সায় দেয় নি। ‘নামঞ্জুর’ গল্পে অমিয়াকে এই সূত্রে মনে পড়বে।
-চার-
বিপ্লবীদের প্রতি গল্পকারের প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। অন্ততঃ গল্পগুলিতে সেই সুর শোনা যায়। চারটি গল্পের সাহায্যে এই দিকটির পরিচয় নেওয়া যাক।
‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পটির মত সরাসরি রাজনীতি নির্ভর কাহিনী আগে তিনি লেখেননি। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ইংরেজ শাসক এবং মালিক-ম্যানেজার বিচারক শ্রেণীর জুলুমের, দম্ভের, অকারণ অত্যাচারের, আইনের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞার, শাসিত জাতির প্রতি প্রবল ঘৃণার নিদর্শন এর মধ্যে বাস্তবভাবে ফুটে উঠেছে।দেশীয় জমিদার-নায়েবদেরদের দাস্যবৃত্তি, অত্যাচারিত হয়েও সাধারণ মানুষের ভীত নীরবতা, দুর্বলের নিরুপায় মিথ্যাচার ও আত্মসমর্পণ-কালোচিত যথার্থ অবস্থা প্রতিবেদন। শশীর মতো কোন কোন নব্যশিক্ষিত ব্যক্তির মানবিক সম্ভ্রমবোধ এবং অস্ফুট স্বদেশী ভাবনা যে ধরনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে দাঁড়াতে চাইত তা সঙ্গীহীন একাকীত্ব এবং অপরিহার্য পরাভব ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার নির্ভুল প্রতিফলন। বরং তার ‘বালকের মতো’ ‘পাগলের মত’ পুলিশ সাহেবকে মারতে আরম্ভ করায় যেন পরবর্তীকালের নির্বিবেচক, আত্মদানে উন্মুখ বিপ্লব তরুণদের অস্ফুট সূচনা লক্ষ্য করা যায়।
এ গল্পের রাজনৈতিক চরিত্র হচ্ছে স্বচ্ছ দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। সমকালে দেশের রাজনীতি ভাবনা অনেক বেশি আপোষপ্রিয় এবং আবেদন-নিবেদনে সীমাবদ্ধ ছিল। এই কাহিনী সংগ্রামী, শত্রুর স্বভাব হননে অভ্রান্ত। এখানে বীর্যের যে রূপ আছে তা পাঠককে উৎসাহী করে।
‘নামঞ্জুর’ গল্প এক আন্দামান ফেরত পুরনো বিপ্লবীকে নিয়ে। সমকালীন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ভন্ডামিকে তার চোখ দিয়ে দেখা হয়েছে এই কাহিনীতে। প্রাক্তন বিপ্লবী এখন অসুস্থ ও ক্লান্ত, কিন্তু পন্থার বিরুদ্ধে তার বা স্বয়ং গল্পকারের নালিশ নেই। বরং নায়কের অন্তর্গত রক্তে এখনো সেই অগ্নিযুগের নিঃশ্বাস-
খদ্দর প্রচারকারিণী কোনো বাঙালি মহিলাকে পুলিশ সার্জেন্ট দিলে ধাক্কা। মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের অসহযোগের ভাবখানা প্রবল দুঃসহযোগে পরিণত হল।
‘শেষকথা’ গল্পের নায়কও বিপ্লবী দলের পাণ্ডা ছিল। আন্দামান যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছিল। ওই পথে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে হঠানো যাবে না এ সত্য সে বুঝেছিল, কিন্তু অসহযোগীদের নরম পথে তার আস্থা হয়নি। বিজ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে দেশের সেবা এবং ব্রিটিশ ভারতে কর্মস্থল না বেছে ওরা দেশীয় রাজে আশ্রয় নেওয়া তার এক ধরনের আত্ম-প্রতারণা সন্দেহ নেই। কিন্তু নবীনমাধব কেরিয়ার তৈরির রাজপথে সহজেই এগুতে পারত, জোগাড় ছিল বিদ্যার প্রভূত পাথেয়। তবু এই প্রাক্তন বিপ্লবী দেশের কথা ভেবে ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের বনে পাহাড়ে খনিজ খোঁজায় আত্মনিয়োগ করেছিল। বিপ্লব পন্থার এই উৎসব শেষ শ্রদ্ধাই জাগায়।
-পাঁচ-
বিপ্লবীকে নায়ক করে শেষ গল্প ‘বদনাম’ । ১৯৪১ সালের ‘প্রবাসী’তে গল্পটি প্রথম ছাপা হয়েছিল। লক্ষ্য করার মতো অনিল প্রাক্তন বিপ্লবী নয় আগের দুটি গল্পের নায়কদের মত। বিপ্লবী পন্থায় দেশোদ্ধার হবে না এমন কোনো ভাবনাও কাহিনীতে স্থান পায়নি। বরং শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যতের কোনো অস্পষ্ট আশার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিজয় ইন্সপেক্টরের উপরে অনিলের জয়ের ব্যঞ্জনা পাঠকের অনুভূতিতে অনেকটা প্রসারিত থাকে।
আরও লক্ষ্য করবার অন্ধবিশ্বাস, বীরপূজা-যে পথ ধরেই হোক এই বিপ্লবী নায়ক ‘জনগণমনঅধিনায়ক’- একজন বিচ্ছিন্ন টেররিষ্ট হয়ে সে থাকেনি।
‘চার অধ্যায়’ পড়ে যারা রবীন্দ্রনাথকে বিপ্লবপন্থার বিরোধী বলে সিদ্ধান্ত করতে চাইবেন তাদের আবার ভাবতে বাধ্য করবে ‘বদনাম’। রবীন্দ্র-কল্পিত এই বিপ্লবী পদ্ধতি কতটা কার্যকর ও মান্য সে বিষয়ে যতই প্রশ্ন থাক, মহাকবির সৃষ্টির অন্তর্নিহিত বাণী যে অহিংস আত্মসমর্পণের নয়, জাগরণের, সে বিষয়ে সাক্ষ্য হয়ে রইল ‘বদনাম’।
* রবীন্দ্রমেলা স্মরণিকা, ত্রয়োবিংশতি বর্ষ, ১৪০২ থেকে পুনর্মুদ্রিত

লেখক পরিচিতি
ক্ষেত্রগুপ্তঃ রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন বিদ্যাসাগর অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে স্ট্রাকচারাল আলোচনা পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। গ্রন্থ- প্রা’চীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন’, ‘মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যশিল্প’, ‘বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস’, ‘সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার’, ‘কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার’, ইত্যাদি।

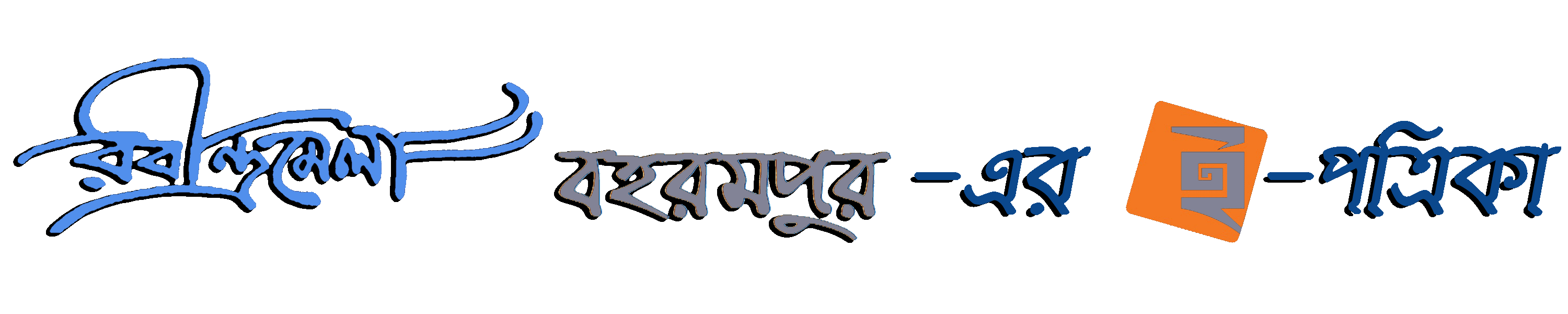
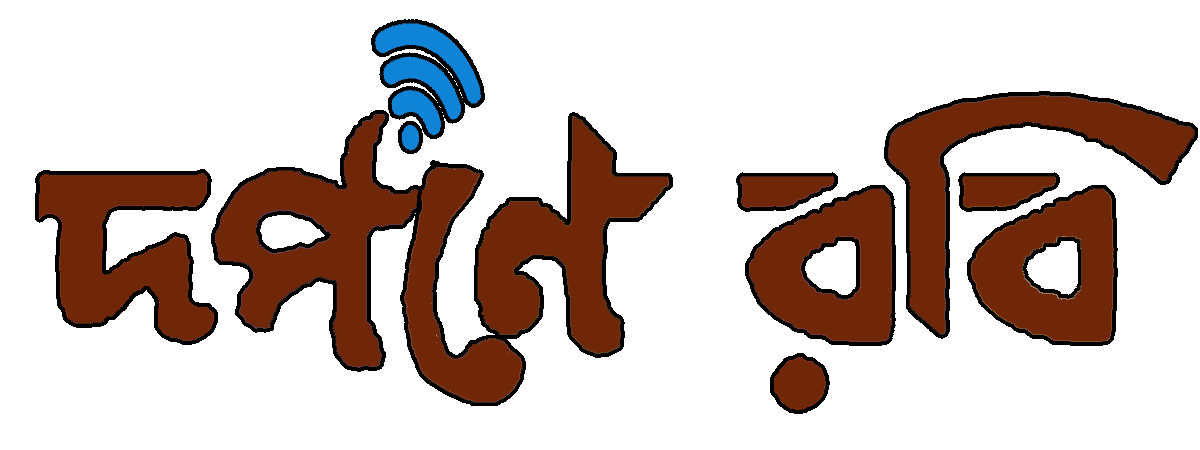



Comments