রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসা ভাবনা
- Oct 11, 2021
- 6 min read
অনির্বাণ দাস

‘চতুরঙ্গ’-এই রবীন্দ্র উপন্যাসে নাস্তিক জ্যাঠামশাই জগমোহন মারা যান মর্মান্তিকভাবে। সেই খবর আমরা জানতে পারি শ্রীবিলাস কথায় -
‘পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না। জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বলিলেন - ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই।’
নিজের উদ্যোগে তখন প্রাইভেট হাসপাতাল খুললেন জগমোহন। শচীশ, শ্রীবিলাস, এরাই ছিল শুশ্রূষার কাজে, সঙ্গে ছিলেন জনৈক ডাক্তারও। যদিও তাদের ভাগ্য প্রসন্ন হয়নি। শ্রীবিলাসের কথায় -
‘আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না। শচীশকে বলিলেন, এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিশ চুকাইয়া লইলাম, কোনো খেদ রহিল না।’
যখন প্লেগের আক্রমণে সবাই দিশেহারা হয়ে নিরাপদ স্থানে পালাচ্ছে, তখন তিনি না পালিয়ে দায়িত্ব নিলেন অসহায় চামারদের নিরাপত্তা বিধানের। নিজের বাড়িতে প্লেগ রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপন করলেন। মুসলমান ও গরিব রোগীদের সেবা করতে করতে নিজেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন মর্মান্তিকভাবে।
দাদার মৃত্যু নিয়ে শচীশের বাবা হরিমোহনের বক্তব্য ছিল অতি সংক্ষিপ্ত – ‘নাস্তিকের মরণ এমনি করিয়াই হয়।’
রবি ঠাকুরের রচিত নানা কবিতায় ও লেখার মধ্যে এভাবেই চলে এসেছে অসুখ বিসুখের কথা।‘পুরাতন ভৃত্য’ কবিতায় পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার মৃত্যুও হয়েছিল গুটিবসন্তে আক্রান্ত মনিবকে সেবাযত্নের মাধ্যমে সুস্থ করে তোলার পর। ‘গোরা’ উপন্যাসে কলেরায় স্বামী-সন্তানহারা হরিমোহিনীর বিলাপে দৈব-বিশ্বাসী বাঙালি সমাজমানসের ছবি তিনি এঁকেছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। কিন্তু আবার ‘দিদি’ গল্পে ওলাউঠা থেকে মুক্তি পেতে গ্রামীণ ‘নেটিভ’ ডাক্তারের চেয়ে শহুরে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকে আস্থা রাখে গ্রাম্য বধূ শশিকলা। ‘দুর্বুদ্ধি’ গল্পে ডাক্তার ওষুধ ছাড়াও বিশ্বাস করে কর্মফলে। ‘ছুটি’ গল্পে ফটিকের অসুখ, ‘দুই বোন’ গল্পে শর্মিলার অসুখ, ‘ভাইফোঁটা’ গল্পে সুবোধের মায়ের যক্ষ্মা রোগ- ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের গল্পে বাস্তববাচিত ভাবে বর্ণনায়িত হয়েছে। তাঁর ‘দুর্বুদ্ধি’ এবং ‘দিদি’ গল্পে এক বালিকা ও এক নারী কলেরায় মারা যায়, দুজনের নামই শশী। ‘শেষের রাত্রি’ গল্পের নায়ক যতীনের মৃত্যু হয় দুরারোগ্য ব্যাধিতে।
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতে প্লেগ বিরাট আকার ধারণ করে। কলকাতাও বাদ যায় নি। প্লেগের ভয়াবহতায় বিচলিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নেমে এসেছিলেন রাস্তায়। নিবেদিতা এবং রবীন্দ্রনাথ- দু’জন সে দিন মহামারি সামলাতে এক সঙ্গে পথে নেমেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়, “সেই সময়ে কলকাতায় লাগল প্লেগ।চারদিকে মহামারী চলছে, ঘরে ঘরে লোক মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রবিকাকা এবং আমরা এবাড়ির সবাই মিলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছি, চুন বিলি করছি। রবিকাকা ও সিস্টার নিবেদিতা পাড়ায় পাড়ায় ইন্স্পেক্শনে যেতেন। নার্স ডাক্তার সব রাখা হয়েছিল।” জোড়াসাঁকোর ধারে কোথাও কি চতুরঙ্গ উপন্যাসের ছায়া পাওয়া গেল?
মহামারির আতঙ্কে কোণঠাসা জনগণকে সারকথা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ ফিরে যান বৌদ্ধ যুগে। সে কালেও সংক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি সমাজ, গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয়েছেন নটী বাসবদত্তা।
‘নিদারুণ রোগে মারী-গুটিকায়
ভরে গেছে তার অঙ্গ
রোগ মসীঢালা কালি তবু তার
লয়ে প্রকারণে পুর পরিবার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিবার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।’ অভিসার
সন্ন্যাসী উপগুপ্ত এই দুঃসময়ে সেবা করে বাসবদত্তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।
রবীন্দ্রনাথের কথায়, “যে সমস্ত রোগের সঙ্গে প্রতিদিন আমাদের ঘর করতে হচ্ছে তাদের সঙ্গে পদে পদে ঘর করতে হলে অসহায় অজ্ঞতা নিয়ে একমাত্র ডাক্তারের দিকেই তাকিয়ে থাকলে চলে—অন্তত কিছু পরিমাণ ডাক্তারের সহযোগিতা না করতে পারলে বাঁচাও নেই। কেননা এদেশে রোগ যত সুলভ, ডাক্তার তত সুলভ নয়।”
আবার ডাক্তারকে নিয়ে তাঁর ব্যঙ্গোক্তি কবিতা এখনো আমাদের মনে দাগ কাটে,
‘পাড়ায় এসেছে এক নাড়ি টেপা ডাক্তার
দূর থেকে দেখা যায় অতি উঁচু নাক তার
নাম লেখে ওষুধের
এ দেশের পশুদের
সাধ্য কি পড়ে তাহা, এই বড় জাঁক তার
যেথা যায় বাড়ি বাড়ি
দেখেছে ছেড়েছে নাড়ি
পাওনাটা আদায়ের মেলে না যে ফাঁস তার।’ খাপছাড়া/৭৬
রবীন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তার শেষ অন্ত না। বরং বলা যায়, তাঁর দীর্ঘজীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে ছিল চিকিৎসাভাবনা।যার বুনিয়াদ সম্ভবত তৈরি হয়েছিল বাল্য শিক্ষার অংশ হিসেবে। দেউড়ির ঘণ্টাধ্বনি বালক বয়সে তাঁর দৈনন্দিন জীবনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রন করতো, তার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন: “অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি, কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে শিরশির করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে।... কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র বসে আছেন মানুষের হাড় চেনাবার বিদ্যে শেখাবার জন্যে।...”।আবার যুবক বয়সে মানবদেহের রহস্য জানার আকাঙ্খায় চলে গেলেন অ্যানাটমির ব্যবচ্ছেদ হলে। অবাক চোখে দেখলেন শব ব্যবচ্ছেদ। আহৃত জ্ঞান থেকে পরে ‘জীবনের শক্তি’ নাম দিয়ে তিনি লিখে ফেললেন হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের কার্যকলাপের কাহিনি। পরবর্তীতে ‘মানব শরীর’, ‘প্রাণ ও প্রাণী’, ‘রোগ শত্রু’ ও ‘দেহরক্ষক সৈন্য’ ইত্যাদি নামে মানব দেহ নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি ডাক্তারি ভাষার অনেক জটিল শব্দের সহজ তর্জমা করেন। ক্ষতিকর কোষগুলোকে গিলে ফেলা ‘ফ্যাগোসাইটিক’ কোষের নামকরণ করেন ‘ভক্ষক কোষ’। আবার ‘ব্লাড প্লাজমা’র নামকরণ করেন ‘বর্ণহীন রস’ ইত্যাদি।
বাংলাদেশের পল্লি-অঞ্চলে বিস্তৃত জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির প্রারম্ভিক রূপরেখা প্রথম তৈরি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়, উদ্যোগে।যার ভিত্তিপ্রস্তর তৈরি হয়েছিল পাবনায়- শিলাইদহে জমিদারি পরিচালনা করতে এসে নৌকায় থাকার সময়ে।তখন তিনি অসহায় দরিদ্র মানুষের অবস্থা দেখে তাদের স্বাস্থ্য সেবার প্রতি আগ্রহী হয়ে তাদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দিতে শুরু করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় খরচ ছিল অপেক্ষাকৃত কম এবং এটি ছিল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিহীন চিকিৎসা ব্যবস্থা। এ কাজ করতে গিয়ে এক সময় শাহজাদপুর কাছারিবাড়ি, পতিসর কাছারি বাড়িতে এবং শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে তিনি ডিসপেনসারিও চালু করেছিলেন।
পদ্মাপারের পতিসরেই লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘এবার ফেরার মোরে!’, যেখানে তিনি জনস্বাস্থ্যের কথা বললেন বড় করে :
‘বড় দুঃখ, বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার!-
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট! এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি!’ চিত্রা
শিলাইদহে থাকাকালীন ডাক্তার জগৎ রায়ের সঙ্গে কবির বন্ধুত্ব হয়। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে কবি লোক পাঠিয়ে জগৎ রায়কে ডেকে আনাতেন। ডা. রায়ের হোমিও চিকিৎসা বিষয়ক বইগুলো কবির খুব পছন্দের ছিল। কবিগুরু হোমিওপ্যাথির চর্চা শুরু করেন ডাক্তার জগৎ রায়ের বই পড়ে। কন্যা মীরাকে এক চিঠিতে লেখেন, “তোরা যখন শিলাইদহে থাকতিস মাঝে মাঝে বিশেষ ব্যামো হলে তিনি (ডা. রায়) আসতেন।” আরেকটি চিঠিতে কবি লেখেন, “আমি তোকে জগৎ রায়ের যে বাংলা বই পাঠিয়েছিলুম সেটা মন্দ নয়। এই বইটা দেখে তোরা যদি চিকিৎসার চর্চা করিস তাহলে ক্রমে ক্রমে পাহাড়িদের মধ্যে ডাক্তারিতে আমারই মতো খ্যাতি লাভ করতে পারবি।”
এবার, চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথের কথা বলি। এক চিঠিতে তিনি প্রশান্ত মহলানবীশকে লিখেছিলেন, ‘তুমি তো জান আমি চিকিৎসাবায়ুগ্রস্ত।’ বহু ডাক্তারি বই তিনি খুঁটিয়ে পড়েছেন, আর নিজের ওপরে ও আত্মীয়-বন্ধুর ওপরে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করা তাঁর প্রায় নেশাই ছিল।
রানি চন্দের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে, " গুরুদেবের গানের বা কবিতার প্রশংসার চেয়ে হাজার গুন খুশি হতেন তিনি, কেউ এসে যদি বলত যে গুরুদেবের ওষুধে তাঁর অমুক অসুখটা সেরে গেছে..."।
বৌমা প্রতিমা দেবী ‘হাঁপানী’ রোগে আক্রান্ত হলে কবি তাঁকে বাড়ির পোষা জন্তু-জানোয়ার ও পাখির ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলতে বলেন। একটি মেডিকেল জার্নাল পড়ে কবি অনুমান করেছিলেন এদের মল-মূত্র অনেক সময় হাঁপানী রোগের কারণ-কবির এই অনুমান আজ পরীক্ষিত সত্য।
আরেকটি ঘটনা। একবার বোলপুরে বেশ কিছু গ্রামবাসীদের মধ্যে ভয়ানক কাশির উপদ্রব দেখা দেয়। কোন কিছুতে কাশি কমছে না। তখন রবীন্দ্রনাথ এর পেছনে কারণটা খুঁজতে থাকেন।হঠাৎ তাঁর মনে হয়, বোলপুর গ্রামটাতো সমুদ্র থেকে অনেক দূরে। তাই এদের হয়তো নুনের অভাব হয়েছে। এই ভেবে তিনি তার চিকিৎসকদের খাওয়ার নুন বায়োকেমিক বড়ি হিসাবে খাওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের পরামর্শ দেন। অবাক কাণ্ড! তাঁর নিদানেই সমস্যার সমাধান!
মৈত্রেয়ী দেবীর ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থ থেকে জানতে পারি, জনৈক গ্রামবাসী কাঁকড়া বিছের কামড়ে যন্ত্রণায় যখন ছটফট করছেন সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সারিয়ে তুলেছেন।
রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কতটা পারদর্শী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় রাণী মহলানবিশের অসুখের সময়। সে সময়ের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার ও আরও অনেক চিকিৎসক-কেউই তাঁর জ্বর কমাতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রানী মহলানবিশ টাইফয়েড থেকে সেরে ওঠেন।
একবার ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথের জ্বর সর্দিকাশি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকে এ্যাকোনাইট ৩০ ও বেলেডোনা ৩০ পর্যায়ক্রমে দিয়ে সুস্থ করে তুলেছিলেন।
মেজো মেয়ে রেণুকার অবস্থা খারাপ হওয়ার খবর পেয়ে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন মেয়েকে দেখার জন্যে। মেয়ের অবস্থা দেখে তিনি খুব ভেঙে পড়েছিলেন। সব ডাক্তার প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেছিলেন। দেখলেন রক্ত ওঠা বন্ধ হয়ে গেছে। কাশি কমে গেছে। বিকারের প্রলাপ বন্ধ হয়েছে। বেশ স্বাভাবিক লাগছে।
বড় মেয়ে মাধুরীলতার ছেলের চামড়ায় একজিমা হয়েছিল, কবি তাকে হোমিও ওষুধ খাইয়ে সারিয়ে তুলেছিলেন। পত্নী মৃনালিনী দেবীর অসুস্থতার সময়েও এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা হাল ছেড়ে দেওয়ার পরে কবি তাঁকে হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক চিকিৎসায় সারিয়ে তুলেছিলেন।
শান্তিনিকেতনে শিশুদের অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে কবি খুব সজাগ ছিলেন। নিয়মিত তাদের সংবাদ নিতেন এবং আশ্রম অধ্যক্ষকেও নিতে বলতেন। এ ব্যাপারে তিনি তার প্রধান সহচর ক্ষিতিমোহন সেনের উদ্দেশ্যে লেখেন, “ছাত্রদের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে তাহাকে যথা সময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়।” শান্তিনিকেতনে ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসার ভার ছিল সুশীল ভক্তের উপর। আর প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা যাতে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে রপ্ত হয় সে ব্যবস্থা করতেও তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন সুশীল ভক্তকে।
একবার ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো মহামারিতেও রবীন্দ্রনাথ কবিরাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শান্তিনিকেতনে এই রোগ যাতে না ছড়াতে পারে, সে জন্য তিনি ‘পঞ্চতিক্ত’ পাচন খাইয়েছিলেন প্রত্যেককে। বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে এই পাচনের কথা জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন, ‘বৌমার খুব কঠিন রকম ন্যুমোনিয়া হয়েছিল। অনেক দিন লড়াই করে কাল থেকে ভাল বোধ হচ্ছে।...কিন্তু ছেলেদের মধ্যে একটিরও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। আমার বিশ্বাস, তার কারণ, আমি ওদের বরাবর পঞ্চতিক্ত পাঁচন খাইয়ে আসছি।...আমার এখানে প্রায় দুশো লোক, অথচ হাসপাতাল প্রায়ই শূন্য পড়ে আছে এমন কখনও হয় না—তাই মনে ভাবচি, এটা নিশ্চয়ই পাঁচনের গুণে হয়েচে।’ এই পাচন ছিল নিম, গুলঞ্চ, বাসক, পলতা ও কন্টিকারির মিশ্রণ।
রোগের নিদান দিয়ে তিনি ক্ষান্ত হন নি। তিনি ভাবনা চিন্তা করতেন কিভাবে রোগকে প্রতিরোধ করা যায়। চিকিৎসা দেওয়ার থেকে রোগটাকে ঠেকানো গেলে সব দিক থেকেই মঙ্গল।Prevention is better than cure –এই আপ্তবাক্যটি কবি বিশ্বাস করতেন। তাই গ্রামবাসীদের এ ব্যাপারে সচেতন করার জন্যে তিনি উদ্যগী হয়েছিলেন।‘আজ মঙ্গলবার। জঙ্গল সাফ করার দিন।’- নালা নর্দমা পরিষ্কার রাখা, মাঠে ঘাটে বাহ্য না করা, পুকুরের সংস্কার করে জল পরিষ্কার রাখার উপর জোর দিতেন তিনি। জনস্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার অন্ত ছিল না। শান্তিনিকেতনের গ্রামে গ্রামে সুষ্ঠু জনস্বাস্থ্য গড়ার কাজে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি থেকে শুরু করে রোগ-প্রতিরোধ, নিরাপদ প্রসব থেকে পোয়াতির পরিচর্যা, ওষুধ দিয়ে সাধারণ অসুখ-বিসুখ সারানো থেকে শুরু করে চিকিৎসার অর্থ সংস্থানের জন্য গ্রামে গ্রামে ‘ধর্মগোলা’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গ্রামগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে, পুকুরগুলোকে পরিষ্কার করে গৃহকার্য্যে ব্যবহারের জন্য, জলনিকাশী ব্যবস্থা উন্নত করার কাজে, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন।তাঁর কাজে উৎসাহী হয়ে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ম্যালেরিয়া মশার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এক ধরণের মশা বিতাড়ন পাউডার তৈরি করেছিলেন, যেগুলো শান্তিনিকেতনবাসীদের খুব কাজে লেগেছিল।
রবীন্দ্রনাথের এই চিকিৎসা ভাবনার উদ্দেশ্য ছিল ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে নিজস্ব সঞ্চয়ের জোরে রোগ তাড়ানো আর রোগ সারানো, যাতে গরিব মানুষকে জনস্বাস্থ্যের সহায়তা পেতে অন্যের সহানুভূতি বা করুণার ওপর নির্ভর করতে না হয়।

লেখক পরিচিতি
অনির্বাণ দাস,রবীন্দ্রমেলার সদস্য।

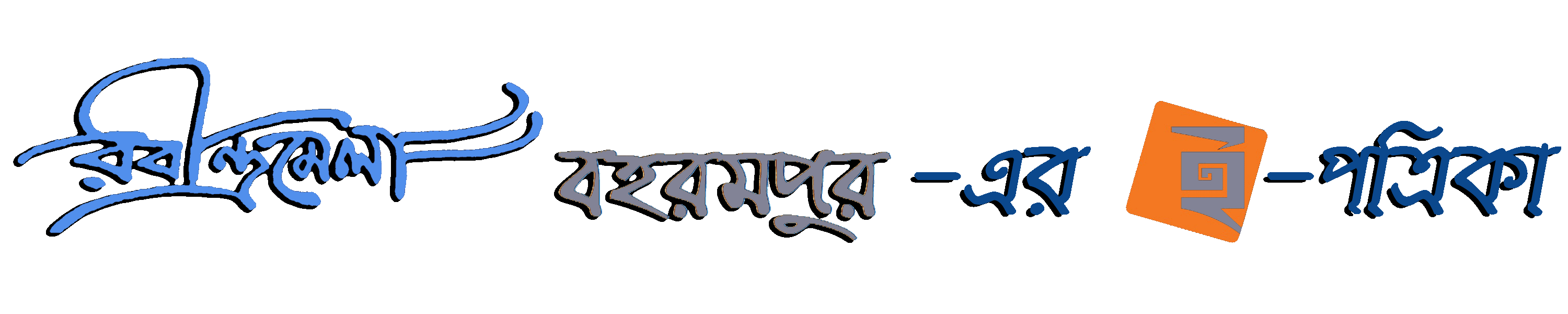
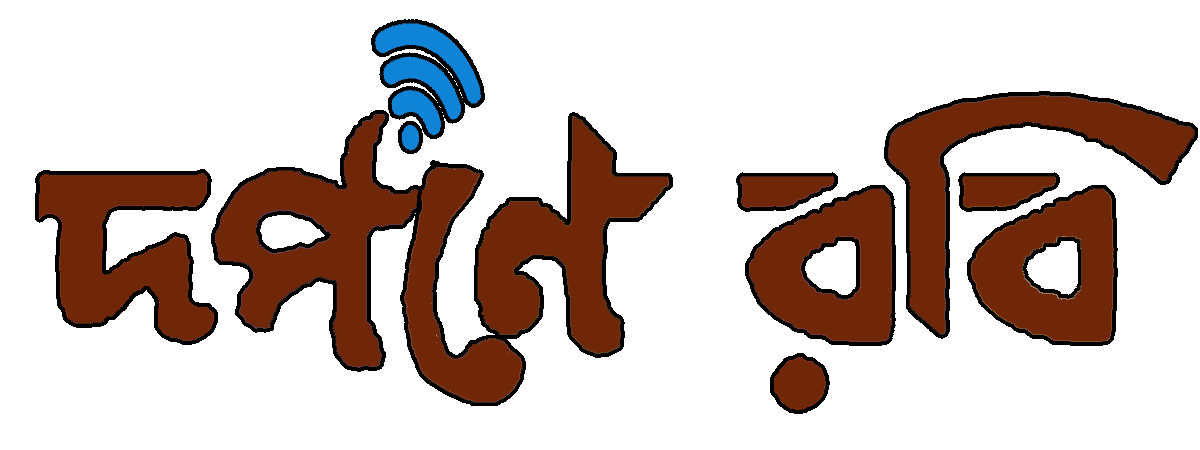







Comments