ঋতুরঙ্গে রবীন্দ্রনাথ
- Aug 8, 2021
- 3 min read
গার্গী মুখার্জি

শ্যাম নামক চাকরটি যখন ছোট্ট রবিকে গন্ডী কেটে, সীতা হরণের ভয় দেখিয়ে গন্ডীতে আটকে রাখার ফন্দি এঁটেছিল, গন্ডীবদ্ধ রবি তখন জানলার খড়খড়ি খুলে, জানালার নীচের ঘাটবাঁধানো পুকুর, প্রাচীরের ধারের চীনা বট, নারিকেল সারিকে নিজের কল্পনার রঙের চিত্রপটে সাজিয়ে সমস্তটাদিন সেই কল্পনার বই এর পাতায় সাজানো সেই কাল্পনিক ছবির দেখেই কাটিয়ে দিত। হয়তো রবির সেই গন্ডীতে আবদ্ধ অবস্থা থেকেই শুরু হয়েছিল তার প্রথম প্রকৃতি প্রেম।
একবার কলকাতায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায়, ছোট্ট রবি তার পরিবারের সাথে ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিলেন গঙ্গাতীরবর্তী পেনেটিতে, ছাতু বাবুর বাগানে। পেয়ারা গাছের অন্তরাল থেকে রবি দিনভর চেয়ে থাকত গঙ্গার ধারার দিকে। কবির ভাষায় "দিনটাকে একখানি সোনালি পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম।"
কবি যে আশৈশব প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন এ ছিল তারই নিছক একটি নমুনা।
প্রকৃতির নানা লীলার সঙ্গে তাঁর মনের ছিল অবিচ্ছেদ্য যোগ।
প্রকৃতি তাঁর কাছে কোনো জড় বস্তু ছিল না, ছিল বাঙময়, কখনো বিষন্ন বিরহী তো কখনো স্নেহময়ী, কখন ভীষণা তো কখনো চঞ্চলা, কখনো বা রুদ্ররূপী ভৈরব, তান্ডবের প্রতীক। ফুল ফল, গাছপালা, নদনদী, পাহাড়, সমুদ্র এমনই শতশত উপাদান তাই বারবার ফিরে ফিরে এসেছে কবির গানে, কবিতায়, রচনায়।
কবি জীবনে কি পান নি তা নিয়ে বিশেষ হিসাব নিকাশ করতে চান নি, বরং তিনি যা পেয়েছিলেন তা ছিল অশেষ, প্রকৃতির দানে পূর্ণ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন কিন্তু বাংলায় ছয়টি ঋতু যেভাবে স্পষ্ট দেখা যায়, অনুভব করা যায়, তা আর বিশ্বের কোথাও তিনি সেইভাবে দেখেন নি, অনুভব করতে পারেন নি।
তাই তো বাংলার নদীর জোয়ারভাটা, মাঠভরা ধানের ক্ষেতে বাতাসের ঢেউ, রাখালিয়া বাঁশি, রাঙা মাটির পথ, সবুজ প্রান্তর তাঁর রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে।
গান ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক কবির সৃষ্টিতে যেভাবে মর্যাদা পেয়েছে, তা তাঁর পূর্ববর্তী, সমকালীন বা পরবর্তী কোনো সংগীত স্রষ্টার সৃষ্টিতে পেয়েছে এমন নিদর্শন নাই বললেই চলে।
শুধু তাঁর প্রকৃতি পর্যায়ের গানেই নয়, প্রেম, পূজা এমন কি বিচিত্র পর্যায়ের গানেও প্রকৃতি ছেয়ে আছে তার স্বমহিমায়। প্রতি ঋতুর সমাগম ও অবসানের মিলন বিরহের বেদনায় কবির মন আনন্দে আকুল ও বিরহে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।
কবির ঋতুপর্যায়ের গান গুলির মধ্যে প্রথম জীবনের গানগুলিতে দেখা যায় ঋতুর গানে ঋতু এসেছিল সানুপঙ্গভাবেই, তাতে অনুভাবনা সংলগ্ন হয় নি তেমন ভাবে। ঋতুকে কবি যেন কিছুটা বিচ্ছিন্ন করেই দেখেছেন। তবে পিতৃ নির্দেশে তিরিশ বৎসর বয়সে যখন কবি জমিদারির কাজে পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে যান তখনই তাঁর নিবিড়ভাবে প্রকৃতিকে চেনাজানা শুরু।
শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০১ সালে। এখানকার প্রকৃতির রূপ পদ্মাপারের মতো রসলালিত না হলেও, এমন কি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপী হলেও, ঋতুচক্রের সমস্ত ঋতুর রূপ, গন্ধ এখানে এমন পরিপূর্ণ যা সহজেই অন্তরের অন্তস্তলে নাড়া দেয়।
৪০ বছর বয়সের আগে কবির রচিত ঋতু সংগীতের সংখ্যা নগন্য, মাত্র এগারোটি। ৪৭ বছর বয়সে ১৯০৮ সালে কবি লেখেন 'শারদোৎসব' ।
শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন " শারদোৎসবের মতো সুন্দর ঋতুর গান এর আগে আমরা পাই না। এই গানেই প্রকাশ পেল যে ঋতুর সঙ্গে একটি আন্তরিক যোগস্থাপনার সূচনা তিনি করতে পেরেছেন"।
শেষ ৪০ বছরে শান্তিনিকেতনের জীবনে তিনি লিখেছেন অসংখ্য ঋতুর গান। আর শেষ ২০ বছরে ঋতু সংগীতে রচনার যে বর্ণনা দিয়েছেন শান্তিদেব ঘোষ তা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় তাঁর ঋতু সংগীতের প্রাচুর্যের সম্পর্কে। শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, " ঋতুর গানের দিক থেকে এই সময়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনে তাঁর এই কুড়ি বছর ব্যাপী সাধনার প্রকৃত পরিচয় এই পর্বেই উন্মোচিত হল। অথবা এ কথা বলা যায় যে, এখন থেকেই তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার সার্থক পরিণতি দেখা দিল"।
কবির প্রকৃতি পর্যায়ের গানের সংখ্যা ২৮৩ টি। যার প্রথম নয় টি সাধারণ ভাবে প্রকৃতির উদ্দেশ্যে লিখেছেন। বাকী গানগুলির মধ্যে ১৬ টি গ্রীষ্মের, ১১৫ টি বর্ষার, ৩০ টি শরতের, ৫ টি হেমন্তের,১২ টি শীতের এবং ৯৬ টি বসন্তের গান।
আসলে কবি মনে করতেন, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল যজ্ঞকান্ড বিশ্বেশ্বর নটরাজের কর্মশালা। শান্তিনিকেতনে ১৩৩৩ সালে দোলপূর্ণিমার রাত্রে নিজে উপস্থিত থেকে নৃত্য -গীত ও আবৃত্তি সহযোগে 'নটরাজ ঋতুরঙ্গ শালা' মঞ্চস্থ করেছিলেন।
এর মর্মার্থে কবি বলেছেন, বিশ্বেশ্বর নটরাজই এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের নিয়ন্ত্রা, যাঁর এক পদাঘাতেই ব্রহ্মান্ড অখন্ডভাবে ঘূর্ণায়মান হয়ে বাইরের আকাশের সমস্ত রূপলোক আবর্তিত হয় এবং যার সামান্য অংশই ঋতু পরিবর্ত্তন রূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। ইনিই নটরাজ, ইনি বিশ্বপিতা নৃত্যকলার অধীশ্বর। তাঁর অপর পায়ের আঘাতে অন্তরলোকে রসলোক উন্মোথিত হয়। বাহির ও অন্তরলোকে এই রস উপলব্ধি করতে পারলে জীবন সার্থক হয় ও বন্ধন মুক্তি হয়। বিশ্বছন্দের একদিকে ধ্বংস ও মৃত্যু অপরদিকে আনন্দ ও প্রাণের প্রকাশ। তিনি প্রকৃতির ফুলে ফলে হাওয়ায় হাওয়ায় যে বিশেষ ঋতু পরিবর্ত্তনের উৎসব চলেছে তাতে সকলকে যোগ দিতে বলেছেন, কারণ তাতেই পূর্ণের আনন্দ পাওয়া যায়।

লেখিকা পরিচিতি
গার্গী মুখার্জী, রবীন্দ্রমেলার সদস্যা।

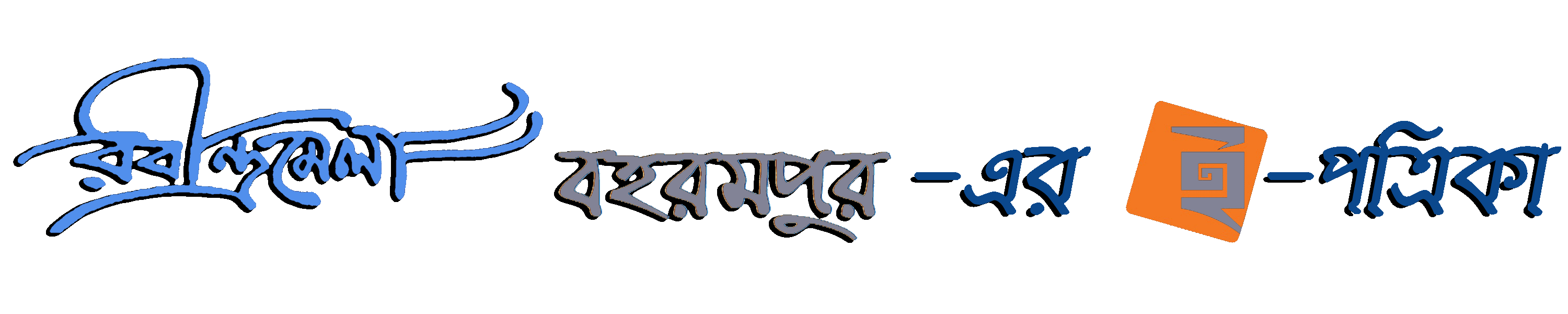
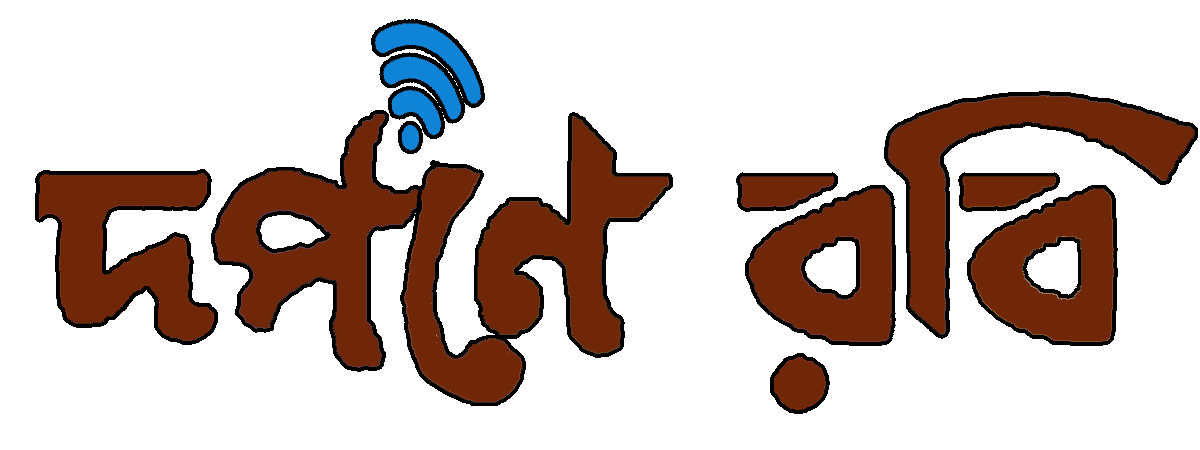







Comments