দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান
- May 9, 2021
- 4 min read
শান্তিদেব ঘোষ

শান্তিনিকেতনে যেখানে আজ ‘মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত সেই দেহলি বাড়ির উপরতলায় ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের সময় থাকতেন রবীন্দ্রনাথ।নীচের তলায় থাকতেন সপরিবারে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেহলি বাড়ির গায়ে লাগা 'নতুন বাড়ি’ নামে গৃহগুলির নানা অংশে যে কয়জন অধ্যাপক থাকতেন সপরিবারে তার একটি অংশে থাকতেন আমাদের বাবা ও মা আমাদের নিয়ে। এ যুগের দেহলি বাড়ির দক্ষিণে দ্বারিক নামে একটি দোতলা বাড়ির একতলায় দিনেন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় রবীন্দ্রসংগীত, উচ্চাঙ্গের হিন্দী কণ্ঠ সংগীত ও যন্ত্র সংগীতের ক্লাস হ’ত। বিদ্যালয়ের অল্পবয়সী ছাত্র হলেও দিনেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পাবার সুযোগ পেয়েছিলাম তখন থেকেই নানা প্রকার উৎসব, অনুষ্ঠান ও নাটকের অভিনয় উপলক্ষ্যে। এক বিশেষ প্রথায় দিনেন্দ্রনাথ আমাদের গান শেখাতেন। তিনি সারা বছর শেখাতেন সকাল ও রাত্রির বৈতালিক গান, বর্ষশেষ, নববর্ষ, বুধবারের মন্দিরের উপাসনা এবং ৭ই পৌষ, খ্রীষ্টোৎসব, মাঘোৎসব, মহাপুরুষের বিদ্বজনের জন্মদিন ও মৃত্যুদিনে উপাসনার জন্য রচিত পূজা পর্যায়ের গন।এছাড়া ঋতু উৎসব, নাটক ও নানা প্রকার সাংস্কৃতিক সভা ও অনুষ্ঠানের উপযোগী গানও তিনি আমাদের শেখাতেন কারণ আমাদেরই তা গাইতে হত।আমরা সবাই শিখতাম দ্বারিক বাড়ির একতলার বড় ঘরটিতে। এইজন্য প্রতিবারই বয়স্ক অল্পবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তিনি একটি বাছাই করা দল তৈরি করতেন।এই দলে সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম আমি। গুরুদেবের চিন্তানুযায়ী প্রবর্তিত এইরূপ একটি অভিনব ও আনন্দদায়ক শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রতিবছর শক্ত ও সহজ, নতুন ও পুরাতনী মিলে নানা পর্যায়ের বহু গান আমাদের শিখতে হ'ত।ভাল করেই শিখতাম। এভাবে প্রবল উৎসাহে বছরের পর বছর সংখ্যায় কয়েক শত গান আমরা শিখেছিলাম নিয়মিত রুটিনের ক্লাসের শিক্ষায় শেখা কখনো সম্ভব ছিল না।দিনেন্দ্রনাথ গান শেখাতেন সন্ধ্যায়, বিনোদন পর্বে। দরকার হলে শেখাতেন ছুটির দিনে, দিনের বেলায়। কখনও কখনও শেখাতেন অপরাহ্নে অন্যান্য ক্লাস বন্ধ রেখে। তার সম্ধ্যাবেলার গানের ক্লাসের গানের অধ্যাপক, অন্যান্য অধ্যাপক কর্মী, অধ্যাপক পত্নী ও বিদ্যালয়ের বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে অল্প বয়সী আমরাও সুযোগ পেতাম। গুরুদেব নিজে আলাদা কোন ক্লাস নিতেন না।।তিনি নতুন গান রচনা করে দিনেন্দ্রনাথকে শিখিয়ে দিতেন আর প্রায়ই শেখাতেন দিনেন্দ্রনাথের ক্লাসে এসে সকলকে নিয়ে, পরে দিনেন্দ্রনাথ আমাদের গলায় ভালো করে সেই গানগুলি বসিয়ে দিতেন। গুরুদেব যখন দিনেন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের গান শেখাতেন তখন আমার বিশেষ লক্ষ্য থাকত গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের প্রতি। গুরুদেব আপন মনে খোলা গলায় নতুন গানটি গেয়ে যেতেন। দিনেন্দ্রনাথ প্রথমদিকে গলা ছাড়তেন না।গুনগুন করে গাইতেন, গুরুদেবের গান শুনে। দেখতাম কাগজে গানের কথার উপরে মাঝে মাঝে কয়েকটি সুর সংক্ষিপ্তাকারে লিখছেন। গানটি আয়ত্তে আসার পর গলা ছেড়ে যখন গাইতেন, তখন গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের মিলিত কণ্ঠে গান আমার মনে এক অপূর্ব আবেগের সঞ্চার করত। আমি নিজে তখন গাইবার কথা ভুলে উভয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম। গুরুদেব তাঁর রচিত পুরানো গানগুলি দিনেন্দ্রনাথের কাছেই শিখে নিতে বলতেন সকলকে। দিনেন্দ্রনাথের গলা ছিল অত্যন্ত গভীর ও উঁচুস্বরের। সকলকে একসঙ্গে নিয়ে যখন গান গাইতেন বা গান শেখাতেন তখন তাঁর সেই ভারী গলা একটি বড় অর্গানের সুরের মত আমাদের গানের দলের গলাকে আবেষ্টন করে রাখত।সেই কারণে দলবদ্ধভাবে গান হাইবার আমাদের কোন অসুবিধাই কখনও হ’ত না।দিনেন্দ্রনাথ এক সময়ে ক্লাসে আমাদের গানের সঙ্গে একটি দেড়-রিডের হারমোনিয়াম বাজাতেন। বড় টেবিল হারমোনিয়াম এবং পাইপ-অর্গানও বাজিয়েছেন উপাসনার গানের সময় মন্দিরে।পিয়ানো যন্ত্রটিও তিনি বাজাতে পারতেন। বৃহৎ আকারের এবং মাঝারি আকারের এসরাজ তিনি বাজাতেন অবলীলাক্রমে। এছাড়া ১৯১৮ সালে দক্ষিণ ভারতীয় বীণাবাদক সংঘমেশ্বর শাস্ত্রীর কাছে সে দেশের বীণা বাজানো শিখেছিলেন। গুরুদেবের গানগুলি তাতে বাজাতেন। তিনি যেমন ছিলেন গুরুদেবের গানের ভান্ডারী, তেমনি ছিলেন তাঁর স্বরলিপিরও। সংখ্যায় গুরুদেবের গানের সবচেয়ে বেশী স্বরলিপি তিনি লিখে গিয়েছেন।অত্যস্ত দ্রুতগতিতে চিঠি লেখার মত সহজে স্বরলিপি লিখতে পারতেন। অনেকের ধারণা গুরুদেবের নতুন গান শিখে নেবার সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথ গানটির স্বরলিপি লিখে গেছেন। একথা ঠিক নয়। তিনি গান শেখার পরই তা করবার কোন চেষ্টাই করতেন না। এমনকি দু'একদিন বা দু'একমাসের মধ্যে নয়। বাংলার নানাপ্রকার লোকসঙ্গীত ও উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সঙ্গীত তিনি জানতেন। ইউরোপীয় সংগীত সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান নাটকীয় ঢঙে গেয়ে শান্তিনিকতনের বালক ও বৃদ্ধ সকলকে আনন্দ দিতেন। দেখেছি গুরুদেবের সঙ্গে সমদক্ষতায় তাঁকে অভিনয় করতে।গুরুদেবের অনুপস্থিতকালে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের নিয়ে নাটকের অভিনয় করানোর দায়িত্ব থাকত তাঁরই ওপরে।
দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বভাব কবি ও সাহিত্যরসিক। বাংলায় গদ্য ও পদ্য তিনি খুব বেশি লিখে যান নি।কিন্তু যেটুকু লিখে গেছেন, তা পড়ে বেশ বোঝা যায় যে, বাংলা ভাষায় তাঁর কতখানি গভীর দখল ছিল।ইংরাজী সাহিত্য ও কাব্য রসানুভূতি ছিল অত্যন্ত প্রখর। ফরাসী ভাষাও তিনি শিখেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্যেও তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব বিভাগের সঙ্গেই তাঁর ছিল অন্তরঙ্গ পরিচয়।তিনি বিদ্যালয়ের বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের নিয়মিত ক্লাস নিতেন। মাঝে মাঝে লিরিক আবেগের কবিতা, গান ও নানা ছন্দে বাস্তব জীবনের নানা কথার ছোট ছোট কবিতাও লিখেছেন নানাজনের চিঠিতে এবং অটোগ্রাফের পাতায়। দেখেছি উৎসাহের সঙ্গে গান রচনা করতে। কয়েকটি গান রচিত হবার পর তিনি থেমে যেতেন। তিনি মনে করতেন ভাবে, ভাষায়, সুরে ও তালে গানগুলি শুনতে হয়তো গুরুদেবের গানের মত। সেই কারণে গান রচনায় তিনি তেমন উৎসাহ পেতেন না। শান্তিনিকেতনের ছোট বড় সকলেরই তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। সকলেই তাঁকে অন্তর থেকে যেমন ভালবাসত, তেমনি শ্রদ্ধাভক্তিও করত।কোন দরিদ্র গ্রামবাসী তাঁর সামনে এসে ভিক্ষার জন্য দাঁড়ালে কোন প্রকার বিবেচনা না করে হাতের কাছে যা থাকত, তাই দিয়ে দিতেন। কোনদিন তাদের টাকাপয়সা দিয়ে, কখনও খাইয়ে দামী বস্তু জুগিয়ে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। গুরুদেবের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং শান্তিনিকেতনের প্রতি তাঁর অনুরাগের গভীরতা যে কতখানি ছিল তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় পরিষ্কার অনুভব করতাম।মাঝে মাঝে ভাবাবেগে বলে ফেলতেন, গুরুদেবের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে বাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে। গুরুদেবহীন শান্তিনিকেতনের কথা তিনি ভাবতেই পারতেন না। কিন্তু সে দুঃখ তাঁকে আর পেতে হয় নি। গুরুদেবের মৃত্যুর ছ’বৎসর পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে ভক্তিপূর্ণ শ্রধাঞ্জলি নিবেদন করার সুযোগ পেয়ে আমি আজ নিজেকে ধন্য মনে করছি।

লেখক পরিচিতি
লেখক বিশ্বভারতীর সংগীত ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ঘনিষ্ঠজন। রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতের অন্যতম নক্ষত্র। তাঁর লেখা গ্রন্থ- ‘রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতীয় নৃত্য’, ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত’, ‘রূপকার নন্দলাল’,‘রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা’, ইত্যাদি।

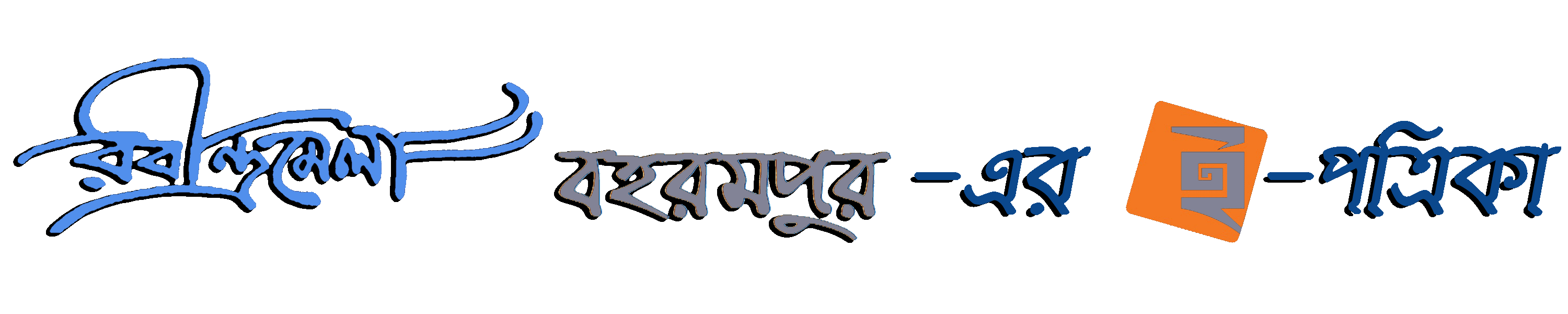
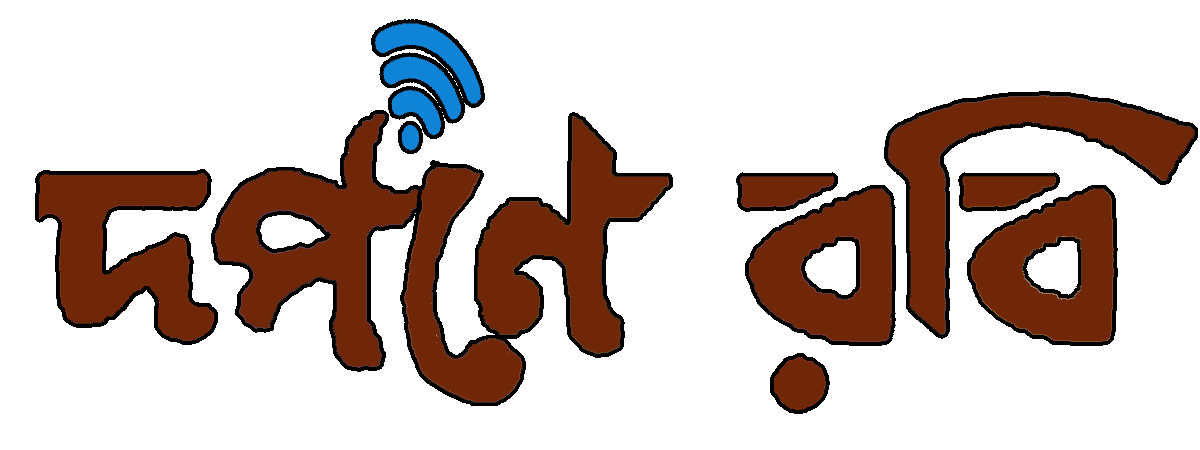



Comments