রবিঠাকুর ও তাঁর জ্যোতিদাদা
- Jan 31, 2021
- 2 min read
গার্গী মুখার্জি

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫ টি সন্তানের মধ্যে পঞ্চম সন্তান ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অষ্টম সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বয়সের দিক থেকে প্রায় ১২ বছরের বড় জ্যোতিদাদার অনেকখানি প্রভাব ছিল কবির উপর।সাহিত্য চর্চা বা ভাবের চর্চা সকল ক্ষেত্রেই কবির প্রধান সহায় ছিল তার জ্যোতিদাদা বা নতুনদাদা।
সবচেয়ে বড় কথা ছিল জ্যোতিদাদা কবিকে কখনো নিছক বালক বলে অবজ্ঞা করেন নি, বরং যে বড় রকমের স্বাধীনতা তিনি দিয়েছিলেন, তা আর কেউ তাকে কখনো দেন নি। সেই স্বাধীনতা কবির ভিতরের সমস্ত সংকোচকে দূর করে দিয়েছিল। কবি যেন তার নতুন দাদার হাত ধরে একটা খোলা আকাশের সন্ধান পেয়েছিল, যে আকাশে নিজেকে ইচ্ছেমতো মেলে ধরা যায়, যেখানে নিজের ডানাগুলো ইচ্ছে হলেই ঝাপটাতে পেরেছেন। এতো স্বাধীনতা দেওয়ার কারণে কেউ কেউ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিন্দে মন্দ করে থাকলেও কবি তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন "প্রখর গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে সময় এই বন্ধনমুক্তি না ঘটলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত।"
মোটের উপর ঠাকুর বাড়ির যে কোনো আদর্শকর্ম ও আন্দোলনের হোতা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। বিচিত্র বিষয়ে আলোচনা ও চর্চায় এঁর আনন্দ ছিল অপরিসীম। এই সমস্ত বিষয়ে তিনি নিজেও ছিলেন উৎসাহী আবার অন্যদের উৎসাহ দানেও ছিল তাঁর আনন্দ। কবিও সংকোচহীন ভাবে যে কোনো ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারতেন তার নতুন দাদার সঙ্গে।
১৮৮০ সালে, বিলাতে ১ বছর পাঁচ মাস কাটিয়ে কবি যখন দেশে ফিরলেন, তখন কবির বয়স ১৯ বছর। দেশে ফিরে নতুন দাদা ও নতুন বৌঠানের আদর ও আপ্যায়ন ভরিয়ে তুলল কবির জীবন। সেই সময় জ্যোতিদাদা দেশি ও বিদেশি সুরের মিশ্রণে নতুন সুর তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে সেই সুরকে কথা দিয়ে বেঁধে রাখায় গুরুদায়িত্ব পড়ল কবি ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উপর। এখান থেকেই কবি সুরের সাথে গান বাঁধার যথার্থ শিক্ষা লাভ করেন।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করলেন মানময়ী গীতিনাট্য। যেখানে ইন্দ্রের ভুমিকায় অভিনয় করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে,আর মদনের ভূমিকায় রবি এবং উর্বশীর ভূমিকায় অভিনয় করলেন কাদম্বরী দেবী। মানময়ীতে গান ছাড়াও গদ্যে কথাবার্তা ছিল। এর একবছর পরেই বাল্মীকি প্রতিভা রচিত ও অভিনীত হয়। যা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে গীতিনাট্য, তাতে সকল কথাবার্তাই গানের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং এ কথা বলাই যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদি পথিকৃৎ হন তবে রবীন্দ্রনাথ তার যোগ্য উত্তরসূরী।
আর একটি কথা না বললে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বলা অসম্পূর্ণ থেকে যায় সেটি হল আকার মাত্রিক স্বরলিপির পদ্ধতি আবিষ্কার।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি নতুন স্বরলিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন যার নাম ছিল 'কসিমাত্রিক'। ‘বালক’ পত্রিকায় ১৮৮৫ সালে সেপ্টেম্বর অক্টোবর সংখ্যায় 'নতুন স্বরলিপি' নামে দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর ঠিক তিন বছর পরে পূর্ব পদ্ধতির সংস্কার করে নতুন পদ্ধতির প্রস্তাব সহ আমরা পাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। 'ভারতী' ও 'বালক'-এ তিনি এই প্রবন্ধ প্রকাশ করেন "গানের স্বরলিপি" নামে। এই পদ্ধতিটি 'সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি' নামে পরিচিত হল। কিন্তু সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিটিতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তিনি পদ্ধতিটির সংস্কার সাধনে ব্রতী হলেন। যার ফলস্বরূপ প্রায় বছর তিনেক পর ১৮৯১ সালে সহজ ও সর্বজনবোধ্য একটি পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করলেন যা 'আকারমাত্রিক' নামে পরিচিত।
যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী,এবং আজও আমরা অস্বীকার করতে পারি না সর্বপরি রবীন্দ্রনাথের গানের উপর এই স্বরলিপি পদ্ধতির প্রভাব চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে।

লেখিকা পরিচিতি
গার্গী মুখার্জী, রবীন্দ্রমেলার সদস্যা।

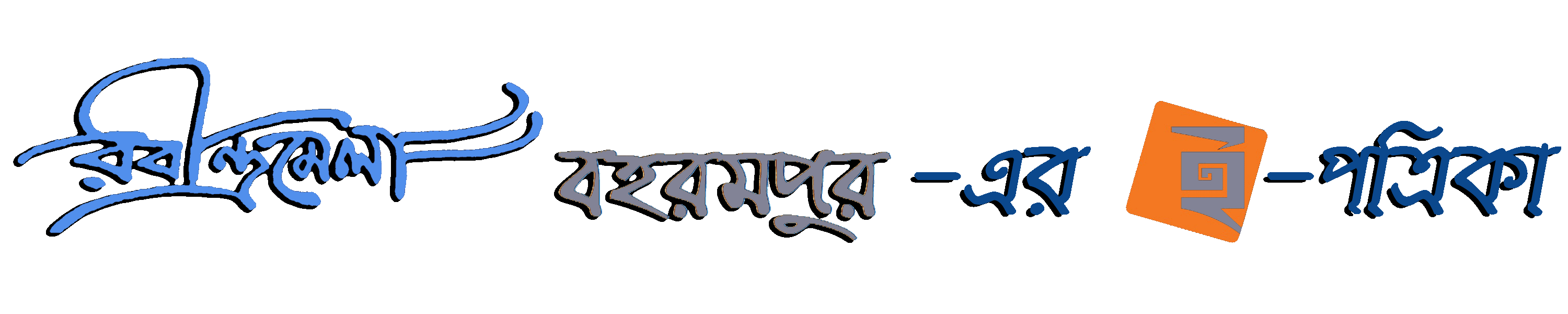
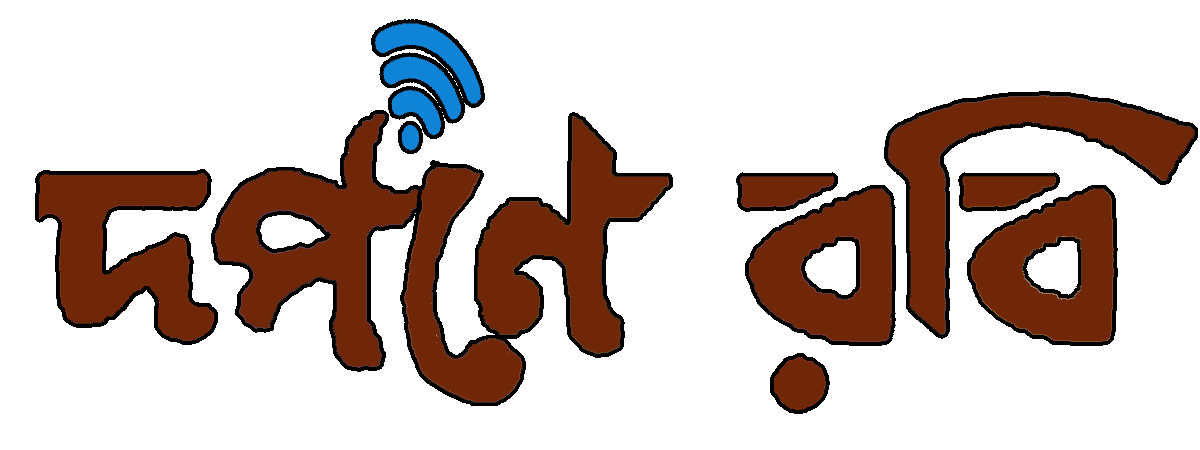







Comments