রবীন্দ্র উপভোগ বনাম রবীন্দ্র অনুরাগ
- Jan 31, 2021
- 4 min read
সুব্রত সরকার

‘আমি পৃথিবীর কবি
যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।’
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই ছিল প্রত্যয়। অবশ্য বাস্তবের সঙ্গে প্রত্যয়ের যে সাযুজ্য ছিল না, এ বোধও ছিল তাঁর সম্যক। তাই তিনি পেরেছিলেন অকপটে স্বীকার করতে,
‘আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে
হয় নাই সে সর্বত্রগামী।’
তথাপি তাঁর আকুতি ছিল, সত্য আকুতি,
‘এই মোর পরিচয়
আমি তোমাদেরই লোক।’
রবীন্দ্রনাথ জনগণের লোক ছিলেন এমন বিজ্ঞাপন বোধকরি অতিভাষণ দোষে দুষ্ট হয়। প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, বিলাইতি আমলা সত্যেন্দ্রনাথের ভ্রাতা, জমিদার রবীন্দ্রনাথ সশরীরে সাধারণ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারবেন- এমনটি আশা করা তাঁর প্রতি অবিচারেরই সমতুল্য। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছেড়ে শিলাইদহের কাছাড়িবাড়ি সংলগ্ন পূর্ববাংলার ভিজে মাটিতে বা শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী গড়ে রাঢ়বাংলার রাঙামাটিতে সাধারণের পদচিহ্নে সামিল হতে সজ্ঞানে চেষ্টিত ছিলেন না তিনি–এমন কথাও বলা যাবে না। আসলে এসব ছিল তাঁর উদার মানবিকতা-সঞ্জাত মানসিক ব্যপ্তির সচেষ্ট ব্যঞ্জনা-যা শুভসূচক হলেও সুফলদায়ী হওয়ার সম্ভাবনাবাহী ছিল না। যা ছিল, তার নাম সত্যাগ্রহ, এক জীবন আদর্শের প্রতি সত্যনিষ্ঠ।
যেদিন ‘বাজিয়ে রবি তোমার বীণে/ আনল মালা জগৎ জিনে’ সেদিনই আমরা প্রথম চিনলাম আমাদের বিশ্বকবিকে, বলা বাহুল্য, বিদেশী মূল্যায়নে। নোবেল প্রাইজ হলো আমাদের কষ্টিপাথর। তাঁর সত্তরতম জন্মজয়ন্তীতে মহানগরীর বুকে চৌরঙ্গীর রাজপথে সুবিশাল মঞ্চে যেদিন তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হল সেদিন হল তাঁর জন-অভিষেক।বঙ্গভঙ্গ রদের সংকল্পে যেদিন কবি স্বরচিত গান গেয়ে জনতার হাতে হাত মিলিয়ে রাখী বেঁধে পথে নামলেন সেদিনই তিনি হলেন জনগণের। সর্বোপরি কবিগুরুর তিরোধনে শোকমিছিলে জনস্রোতের যেদিন বাঁধ ভাঙলো, জনতার পায়ে পায়ে যেদিন চলমান কলকাতা প্রত্যক্ষ হল সেদিন জনগণ হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের। কবির মনোবাসনা পূর্ণ হল তাঁর মহাজীবনে নয়, মহামরণে। পৃথিবীর আর কোনো কবির এমন সৌভাগ্য হয়েছে বলে জানিনা।এই স্বীকৃতি স্বর্গাদপি গরিয়সী। বাঙালীর জাতীয় জীবনে শুধু পঁচিশে বৈশাখ নয়, বাইশে শ্রাবণেরও একটা স্থায়ী মর্যাদার আসন আছে।
1961 সালে কবির জন্মশতবর্ষে সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল মরণোত্তর কবিকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবার; সুযোগ ছিল বলবার, ‘নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।’ প্রয়াস যে হয় নি একথা বলি না’ তবে সে প্রয়াস সর্বান্তঃকরণ ছিল–মানতে বাঁধে। বিশ্বভারতী থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে রাজ্য সরকার রবীন্দ্র রচনাবলী ছাপলেন বিদেশী সরকার কর্ত্তৃক বিনামূল্যে প্রদত্ত কাগজে, সকলের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিতে। পারলেন কি? ঐ রচনাবলীর মূল্য কতটা সুলভ ছিল তখনকার মূল্যমানে, সর্বসাধারণের নাগালে? অথচ 1972 সালে বাংলাদেশ তো পেরেছিল ইতরজনের জন্য নিউজপ্রিন্টে রবীন্দ্র রচনাবলী ছেপে প্রকাশ ও প্রচার করতে।কিন্তু আমাদের এপার বাংলায় রবীন্দ্রনাথ রয়ে গেলেন ভদ্রলোকেদের পড়ার ঘর বা বৈঠকখানার শো-কেসে।আমরা কবিগুরুকে মুক্তি দিলাম 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে।' পাছে শো-কেসের সৌকর্য নষ্ট হয় তাই ফি বছর পঁচিশে বৈশাখ ছাড়া অন্য দিনগুলিতে বইগুলি নাড়াচাড়া করতেও ভুলে গেলাম।তাই বলে রবীন্দ্রনাথ অবহেলিত রইলেন এমন কথা বলা ঠিক হবে না। যখনই প্রয়োজন হয়েছে, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, তখনই রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়েছে, তাঁকে স্মরণ করেছি, তাঁর শরণ নিয়েছি। সোজা কথায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা ব্যবহার করেছি আমাদের দরকার মতো খণ্ড ক্ষুদ্র করে। রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করা সহজসাধ্য তা বলি না কিন্তু তাই বলে অন্ধের হস্তি দর্শনকে কি সত্য রবীন্দ্রচর্চা বলে?সত্যি কথা বলতে কি আমাদের এই মেকি রবীন্দ্রচর্চা তথা রবীন্দ্র প্রয়োগে একটা পাটোয়ারী বিবেচনা ছিল। একে রবীন্দ্র উপভোগ বা Rabindra consumption বলা যায়। অর্থের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ, প্রচারের প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ, ব্যবসার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ মায় অনূঢ়া পাত্রীর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথও দিব্যি রবীন্দ্রাগ্রহ বা রবীন্দ্রানুরাগ বলে চালিয়ে দেওয়া গেছে। চলেছে এখনো প্রায় সমভাবেই। আগরবাতির প্রচারে দু-ছত্র রবীন্দ্রনাথ, দীঘার সমুদ্র সৈকতে পর্যটক আকর্ষণে এক কলি রবীন্দ্রনাথ, বাংলার তাঁতের শাড়ির বর্ণনায় আধ-স্তবক রবীন্দ্রনাথ, এইরকম।অধুনা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক রবীন্দ্রবাণী 'মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'-এর প্রচারকেরা নিজেরা কতখানি মাতৃভাষায় রবীন্দ্র রচনার পাঠ নিয়মিত নেন জানতে ইচ্ছা হয়। কৌতূহল জাগে, প্রচারধর্মী রবীন্দ্রজয়ন্তী বা অনুরূপ বিবিধ রবীন্দ্রচর্চা নির্দশক প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক এবং প্রায়শঃই কেতাদুরস্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানেরর উদ্যোক্তা উদ্বোধক উচ্চ পদাধিকারীদের সত্য রবীন্দ্রানুরাগের পরিমাপ বিষয়েও।ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপকদের তবু সাধুবাদ দিই ক্রেতাসাধারণের রবীন্দ্ররুচির উপর ভরসা দেখে। বা অন্যভাবে বলা চলে তারা অন্ততঃ যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করেছেন আমাদের রবীন্দ্ররুচি করে নিতে।আমরা উদ্বুদ্ধ হই বা না-ই হই।
রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল,'বাঙালি কে আমার গান গাইতেই হবে', সে বিশ্বাস তাঁর ব্যর্থ হয়নি। রবীন্দ্র রচনার শতধারার যে দিকটি ব্যাপকতম আদরণীয়তা লাভ করেছে তা' নিঃসন্দেহে তাঁর সঙ্গীত। বাংলার এপারে ওপারে ঘুম ভাঙ্গে ঘুম আসে রবীন্দ্রসঙ্গীতে। সেই অর্থে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের 'সোনার কাঠি রূপোর কাঠি।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রচিত গানের সংখ্যা যেখানে আড়াই হাজারেরও অধিক সেখানে আমরা প্রায় নিয়মিত মোটের উপর কতগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পাই?রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অসংখ্য, পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তনের সংখ্যাও অগুণতি।তবু যে বিশেষ কিছু সংখ্যক মাত্র গানেরই পুনরাবৃত্তি চলে তার মূলেও কি পাটোয়ারী বুদ্ধি কাজ করে না? এবং তাদেরও অধিকাংশের আবার অরাবীন্দ্রিক উচ্চারণ, নাকি ঢঙ, দন্ত্য সুর। গীতাঞ্জলির গীত থাকলেও অঞ্জলি থাকে না। অর্থাৎ ভাবের ঘর ফাঁকাই থেকে যায়।গানের প্রাণটি মারা পড়ে।
রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা তার কবিতায়। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আবশ্যিক পাঠ্যক্রমে রবীন্দ্র কবিতা পড়তে বাধ্য হয়। বাধ্যতার ব্যাপারটি থাকলেও তারা কিন্তু আগ্রহের সঙ্গেই পড়ে, আনন্দও পায়। ইদানিং আবৃত্তি অনুশীলনের একটা বারোয়ারি আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভালো হতো যদি সঞ্চয়িতার মতো কবিতা সংকলনগুলি এইসব কচিকাঁচা পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের কাছে সহজলভ্য হত।
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাসের নাটকায়ন ও চলচ্চিত্রায়ন সেগুলিকে সাধারণের কাছে কিছু পরিমাণে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে সন্দেহ নাই। তবু সাধারণভাবে ঝোঁকটা রয়ে গেছে তার উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলীর অস্পৃশ্যতার দিকেই। তুলনায় রবীন্দ্র গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য অনেক বেশিই জনমনোহারী।এ তাঁর লিখনের গুণে অথবা আমাদের রসাস্বাদনের যোগ্যতাগুণেও হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভার যে দিকটি সর্বাধিক অনাদৃত তাহলে তার চিত্র শিল্প, বোদ্ধাদের মতে যা নাকি তার বহুমুখী প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশের স্তর।বস্তুতঃ চিত্র ভাস্কর্যের ভাষা এবং ব্যাকরণ আমাদের অনেকেরই আয়ত্তাধীন নয়।আমাদের এই অজ্ঞতা বা অক্ষমতা কবির উপলব্ধিতে ছিল। তাইতো তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে অকপটে লিখতে পেরেছিলেন,'আমার ছবি এদেশকে দেখাইনি। এদেশের অধিকাংশ লোকই ছবি দেখতে জানে না।' যদিও রবীন্দ্রনাথের 'চিত্র ভারতী' ভারত সরকার কর্তৃক জাতীয় সম্পদ হিসেবে ঘোষিত তথাপি সেগুলি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের যথেষ্ট উদ্যোগ নাই।'ন্যাশনাল গ্যালরি', 'ইনট্যাক' বা 'ইউনেস্কো'র কোন সাহায্য চাওয়া হয় না এই অমূল্য রত্নভান্ডার রক্ষার জন্য। অযতনে অনাদরে সেগুলি নষ্ট হতে বসেছে। এই আমাদের রবীন্দ্র উত্তরাধিকার!
বিঃদ্রঃ- এই নিবন্ধটি লেখকের ইচ্ছানুসারে 'কর্ণসুবর্ণ পাক্ষিক, ঊনবিংশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা ২ রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৯' থেকে পুনর্মুদ্রিত।সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতাঃ প্রয়াত সম্পাদক-প্রকাশক পীযূষ কান্তি চন্দ্র।এই প্রবন্ধটি লেখকের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আত্মপ্রকাশ, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বাংলা নববর্ষ 1427 সাল' সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

লেখক পরিচিতি
সুব্রত সরকার, রবীন্দ্রমেলার শুভানুধ্যায়ী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

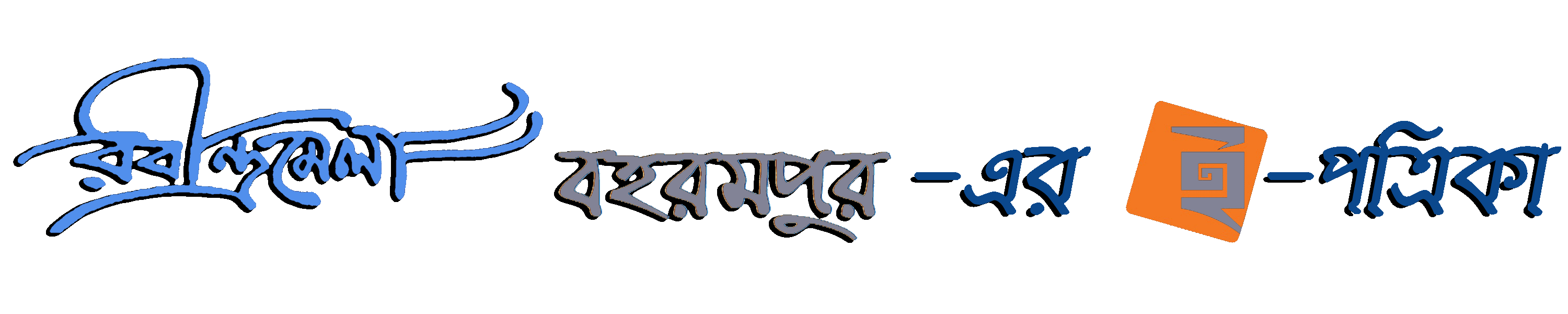
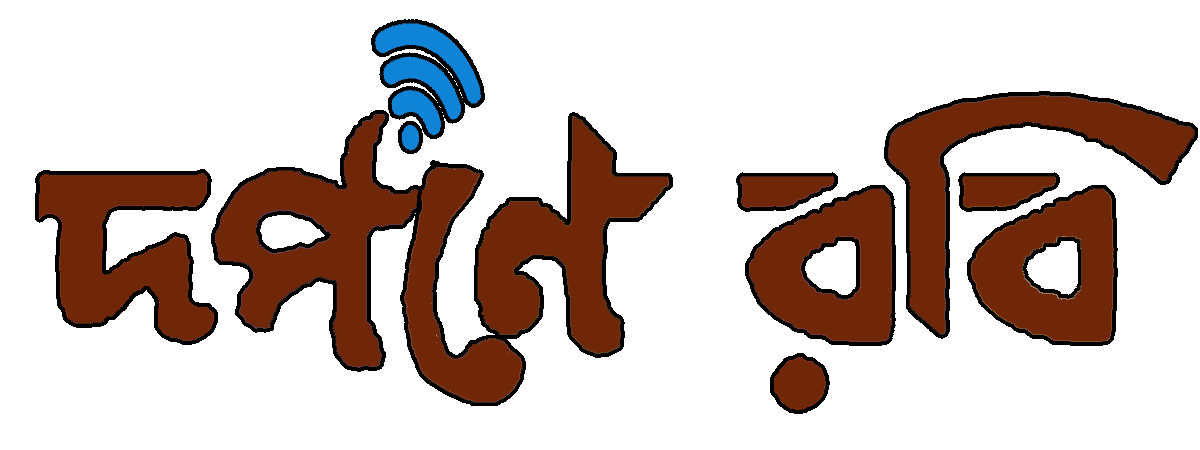







Comments