রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিদাদা – মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ
- Jan 31, 2021
- 3 min read
পাপিয়া বসাক

ঠাকুরবাড়ির আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি যদি আপামর বাঙালীর প্রাতঃস্মরণীয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হন তাহলে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র অবশ্যই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদা, সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদানন্দিনীর ‘নতুন’ এবং ইন্দিরাদেবীর ‘নতুনকা’ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মহর্ষি এবং সারদাদেবীর পঞ্চম পুত্র।
রবির জ্যোতিদাদার জীবনে এঁদের অন্য দুই ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রভাব ছিল। এঁদের উৎসাহ এবং ব্যবস্থাপনাতেই জ্যোতিদাদা একাধারে ব্যায়াম, কুস্তি, সাঁতার-এ যেমন পারদর্শী হয়ে ওঠেন, তেমনই নাট্য, সংগীত, চিত্রকলা বিজ্ঞানশিক্ষা, ভাষাশিক্ষাতেও তাঁর অগাধ জ্ঞানের পরিচয় আমরা পাই।
আন্তঃজালের কল্যাণে আজ আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী কারও অজানা নয়। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে বলা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি সহজেই পাঠককে বুঝিয়ে দেয় কি পরিবেশে যথাক্রমে ‘জ্যোতিদাদা’ এবং তাঁর ‘রবি’ বড় হয়েছেন। এই রচনার মূল বিষয় জ্যোতিদাদার জীবনী অনুসন্ধান নয়, বরং রবির জীবনে এবং তৎকালীন বঙ্গসমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা এবং প্রভাবই এই রচনার মূল আলোচ্য বিষয়।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন মানুষ যিনি না থাকলে বাঙালী গীতা রহস্যের হদিশ পেত না। সংস্কৃত নাটকের বিশাল ভাণ্ডার অধরাই থেকে যেত। বঞ্চিত থাকত পাশ্চাত্য সাহিত্যের রস আস্বাদন থেকে।
বাঙালীর দিনলিপিতে রঙ্গালয়কে জনপ্রিয় করে তুলতে গিরিশ ঘোষেরও আগে আসবে জ্যোতিদাদার নাম। তাঁর কাছেই বাঙালী স্বদেশীয়ানার প্রথম পাঠ নেয়। অরবিন্দ ঘোষের হাত ধরে তিনিই প্রথম প্রথম বাঙ্গালীকে ‘গুপ্ত সমিতি’ গড়তে শেখান। এবং সেটা বিপ্লবী যুগ শুরু হওয়ার অনেক আগে। তাঁর নীলচাষ, পাট এবং স্টিমারের ব্যবসা প্রমাণ করে যে বাঙালী চাইলে প্রতিপক্ষ ইংরেজ বেনিয়াদের পাততাড়ি গোটানোর ব্যবস্থা করতে পারে।
বিদ্দজন সমাগম, সঞ্জীবনী সভা, সারস্বত সমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্যসেবার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আর সর্বোপরি গড়ে দিয়েছিলেন বাঙালীর তথা ভারতবর্ষের গর্বের রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ ‘মেন্টর’ যদি কেউ থাকেন, তিনি হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আরও একটি গুণ হল ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা। সেই সময় ঠাকুর বাড়িতে যে বড় বড় গায়করা আসতেন তাঁদের মধ্যে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজচন্দ্র রায় ও যদুভট্টকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাছে পান এবং তাঁদের সাহচর্যে অপূর্ব সব ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। কিন্তু তিনিই আবার বলেন, তাঁদের পরই ‘রবীন্দ্রনাথের আমল। তাঁহার অসামান্য কবি প্রতিভা এখন ব্রহ্মসঙ্গীতকে পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে।’ রবির সাথে জ্যোতিদাদার সম্পর্কের এ এক আশ্চর্য দিক।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম সৃষ্টিকর্ম ‘সঞ্জীবনী সভা’ স্থাপন। এই সভাই কালক্রমে রবীন্দ্রনাথকে ‘নব-ভানু’ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।
ঠাকুর বাড়ির সংগীত বিপ্লবে মূল ভূমিকা ছিল জ্যোতিদাদার। তিনি পিয়ানো, ভায়োলিন, হারমোনিয়াম, ও সেতার বাজানোতে দক্ষ ছিলেন। তাই তিনি সুরারোপ করতেন এবং পিয়ানো বাজাতেন। এবং অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ সুরগুলিতে কথা যোগ করতেন। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য ‘মায়ার খেলা’য় ব্যবহৃত ২০টি গানের সুরকার তাঁর জ্যোতিদাদা।
রবির জ্যোতিদাদা ১৯২৫ সালের ৪ঠা মার্চ তাঁর ৭৬ বছর বয়সে মারা যান। জ্যোতিদাদা তাঁর রবির থেকে আনুমানিক ১২/১৩ বছরের বড়ো ছিলেন। রবি তাঁর কর্মময় ৮০ বছরের জীবনে যা যা কর্মকাণ্ড করেছেন তার প্রায় সবক্ষেত্রেই তাঁর জ্যোতিদাদার প্রভাব খুব স্পষ্ট। প্রদীপ জ্বালানোর জন্য ‘সলতে পাকানো’ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেই ‘সলতে পাকানো’র কাজটি আজীবন করে গেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবং সারাজীবন ধরে জায়গা ছেড়ে গেছেন প্রাণাধিক প্রিয় রবি-র জন্য। জ্যোতিদাদার রবি বা রবির জ্যোতিদাদা – একটি মুদ্রার দুই পিঠ- অবিচ্ছেদ্য – চিরকালীন।
এই রচনার যবনিকাপাত হবে জ্যোতিদাদার রচিত কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত উল্লেখ-এর মাধ্যমে।
১। আজি বিশ্বজন গাইছে মধুর স্বরে (খাম্বাজ/ সুর ফাঁকতাল)
২। কেন ম্লান নিরানন্দ? ডাক না প্রভু প্রেমময়ে! (ইমনকল্যাণ/ ধামার)
৩। ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী (ঝিঁঝিট /একতাল)
৪। বিমল প্রভাতে, মিলি এক সাথে, বিশ্বনাথে কর প্রণাম (ভৈরব/ত্রিতাল)
৫। অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলো না তাঁয় (আলাইয়া/ ত্রিতাল)
ধন জন জীবন তাঁরি করুণা,
তাঁর করুণা মুখে বলা নাহি যায়;
এত যার করুণা তারে কি ভুলিবে?
তাঁরে ছাড়িয়ে ভবসাগরে ত্রাণ কোথায় ?
“ জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতাম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনও বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্ত বিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার ‘পরে কৃতিত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম করতেন, তাহলে ভেঙেচুরে, তেড়েবেঁকে যা হয় একটা কিছু হতুম, সেটাই হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনক হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।”
ঋণঃ ডঃ শিশির কুমার দাস, উইকিপিডিয়া

লেখিকা পরিচিতি
পাপিয়া বসাক, রবীন্দ্রমেলা বহরমপুরের সদস্য

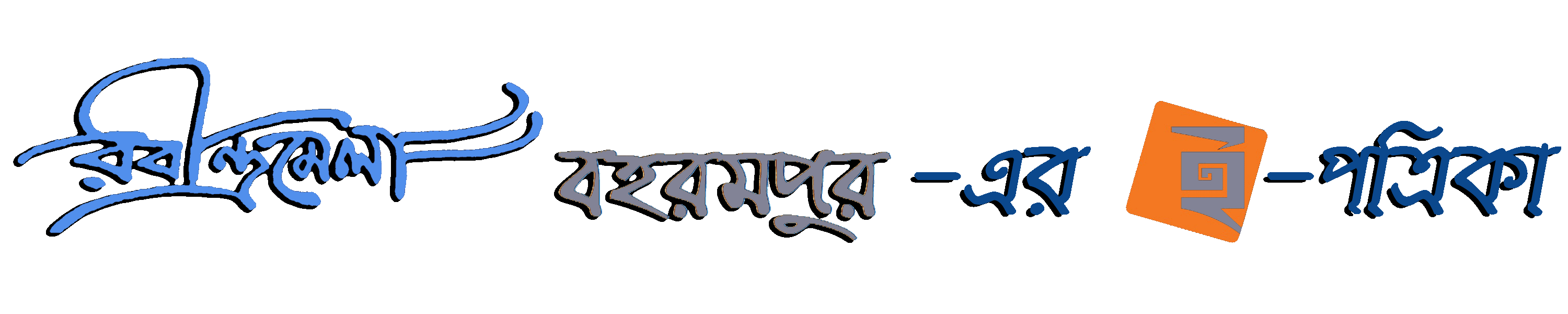
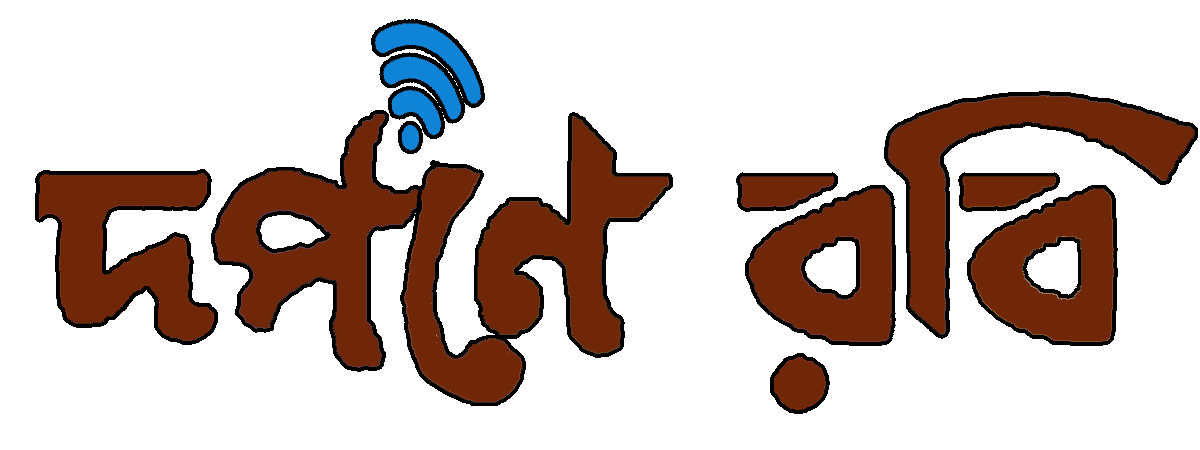







Comments