রবীন্দ্রনাথ ও নারী প্রগতি
- Oct 11, 2021
- 4 min read
সুমনা সরকার

১৯০১ সালের ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও জমিটি কিনেছিলেন তার বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুর এর কাছে ১৮৮৩ সালে। পরে জায়গাটির নাম দেন শান্তিনিকেতন।বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়েছিলেন।
সেই সময় বিদ্যালয়ের খরচের জন্য ঠাকুরবাড়ি থেকে আলাদা করে মাসোহারা পেতেন রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যালয়ের প্রথম পাঁচ জন ছাত্রের অন্যতম ছিলেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
এদিকে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাড়ছে। বঙ্গভঙ্গ নিয়ে সকলেই সরব। সবাই স্বদেশী জিনিসের দিকে ঝুঁকছেন।বিলেতি দ্রব্য বর্জন চলছে পুরোদমে। অরবিন্দ ঘোষ পরিকল্পনা করছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। কিন্তু নানা কারণে এখনও ফলপ্রসূ হয়নি। এরই মাঝে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৮ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন বিশ্বভারতীর। ঠিক তিন বছর পর ১৯২১ সালের এই দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে পথচলা শুরু হলো সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের।
রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় স্থাপন করলেন কিন্তু খরচা আসবে কোথা থেকে? ইতিমধ্যে তিনি তার নোবেলপ্রাপ্তির প্রায় পুরো টাকাটাই দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরীর কাজে। কিন্তু আরো টাকা চাই।খরচ অনেক। তিনি সে সময় অর্থ চিন্তায় বেশ জর্জরিত।
কিভাবে টাকার উপায় হতে পারে আলোচনার জন্য শান্তিনিকেতনে নিজের কাছের জন দের নিয়ে একটা ছোট সভা ডাকলেন উপস্থিত সকলের মতামত চান তিনি অনেকেই গুরুদেবকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিচ্ছেন। সবার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা।
গুরুদেব বুঝলেন সভার পরিবেশ বড় বেশি গুরুগম্ভীর হয়ে উঠছে। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন,"আহা! তোমরা এতো ভাবছো কেন টাকা পাবার একটা অতি সহজ উপায় আছে। "সবাই কৌতুহল নিয়ে জানতে চাইলেন কি সে উপায়? গুরুদেব এবার সেখানে উপস্থিত রানি চন্দকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে সবার দিকে ফিরে বললেন," মাত্র সোয়া পাঁচ আনা খরচ"।
গুরুদেবের কথা শুনেই লজ্জায় পড়ে গেলেন রানী চন্দ। তিনি বুঝে নিয়েছেন এবার গুরুদেব ঠিক কি বলতে বলেছেন। আসল ঘটনা হলো রানী চন্দ একবার খুব আগ্রহ নিয়ে গুরুদেব কে মা মঙ্গলচন্ডীর ব্রত কথা শুনিয়েছিলেন। বাংলার ঘরে ঘরে সেই সময় ব্রত বেশ প্রচলিত ছিল। ব্রতের কথাতে বলা আছে নিষ্ঠা ভাবে এই ব্রত উপবাস করলে নির্ধনেরও ধন হয় আর বলেছিলেন" পুজোর খরচও বেশি নয়, মাত্র সোয়া পাঁচ আনা"।
এখন আসা যাক রানী চন্দের কথায়ঃ
কখনো শুনেছেন রবীন্দ্রনাথ কারো বিয়ের পৌরোহিত্য করেছেন? শুনতে আশ্চর্য লাগলেও সেটি ছিল ১৯৩৩ সালে। সেবার রবীন্দ্র সপ্তাহ উদযাপন এর জন্য ডাক এসেছে মুম্বাই থেকে।রবীন্দ্রনাথ গিয়েছেন সাথে প্রায় জনা ৪৫-এর একটি দল। সেই দল রানী চন্দ আছেন। তিনি তখন রানী দে।এবং সাথে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তির ব্যক্তিগত সচিব অনিল চন্দও সেই দলে উপস্থিত। বিশ্বভারতীর সূত্রেই শান্তিনিকেতনেই একে অপরকে চেনাজানা। দুজনের বিয়েও প্রায় ঠিক। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেছে অনিল চন্দের পরিবার বিয়ে এখন হয় কিনা সেটিই একটি বিরাট প্রশ্ন। গুরুদেব সব শুনেছেন কিন্তু কোনো মন্তব্য করেননি।
রবীন্দ্রনাথ মুম্বাই চলেছেন। হঠাৎ বর্ধমান স্টেশনে দেখা গেল রানী দে আর অনিল চন্দ হাজির। তারাও বিয়েতে দু'বাড়ির মনোমালিন্য ভুলে রবীন্দ্রনাথের সাথে যাত্রায় শামিল হতে চায়।
মুম্বাই পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ উঠলেন পূর্বনির্ধারিত টাটা প্যালেসে।বাকিরা সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা মত রানী দে উঠলেন পুরুষোত্তম ত্রিকোমদাসের (সেই আমলের নামজাদা আইনজীবী) স্ত্রী বিজু বেনের বাপের বাড়িতে। তখন বিজু বেন শান্তিনিকেতনের কলাভবন এর ছাত্রী।
যেদিন তাঁরা মুম্বাই পৌছলেন সেদিন বিকেলেই রবীন্দ্রনাথ খবর পাঠালেন রানী কে ভালো করে সেজেগুজে তাড়াতাড়ি টাটা প্যালেসে চলে আসতে।
কবিগুরু সেজে আসতে বলেছেন, এদিকে রানী তাড়াহুড়োয় একটার বেশি শাড়ি আনেননি। গত কয়েকদিন এই একটি শাড়ি পড়েই কাটছে। চিন্তায় পড়লেন তিনি। অনেক কষ্টে একটা শাড়ি যোগাড় হল। সেই শাড়ি পরে এবং মাথায় একটু ফুল জড়িয়ে হাজির হলেন রানী টাটা প্যালেসে।
গিয়ে দেখলেন গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি আর গলায় লম্বা জুঁইয়ের মালা পড়ে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। ডেকে পাঠানো হয়েছে অনিল চন্দকেও।দরানী আর অনিল কে নিজের সামনে বসালেন কবি।
ঘরে তখন উপস্থিত সরোজিনী নাইডু, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেনও।গুরুদেবের নির্দেশে নন্দলাল বসু হলেন কন্যাপক্ষ শান্তিনিকেতনে রানী তাঁর প্রিয় ছাত্রী। ক্ষিতিমোহন সেন হলেন বরপক্ষ।
রবীন্দ্রনাথের কড়া হুকুম ঘরে এই সময় যেন কেউ না ঢোকে।সেই কারণে দরজায় পাহারায় রইলেন হরেন ঘোষ।(তিনি মুম্বাইতে এই রবীন্দ্র সপ্তাহ অনুষ্ঠানের মূল পরিকল্পনাকারী)।
দুজনকে সামনে বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুরু করলেন বৈদিক মন্ত্র পাঠ। তারপর নিজের গলা থেকে ফুলের মালা খুলে তাদের হাতে দিলেন। তাই দিয়েই হল মালাবদল এবং সম্পন্ন হলো বিবাহ।
বিয়ে তো হল কিন্তু সকলকে খবর দেয়া হবে কিভাবে? মুম্বাইয়ের মেয়র এর বাড়িতে সেদিন সন্ধ্যেবেলা নৈশভোজের আমন্ত্রণ কবি আর তার সমস্ত সাথীদের।সেখানে সকলে হৈ হৈ করছে কবিকে নিয়ে। হাজির সংবাদমাধ্যমও। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ সকলকেই চমকে দিয়ে বললেন আজ আর তাঁর দিন নয়, এদের বিয়ের দিন। নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করার দিন।
তারপর দিন সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমস্ত ভারত জেনে গেল তাদের বিয়ের খবর।
রানী চন্দের জন্ম মেদিনীপুরে। তাঁর বাবা ছিলেন সেই আমলের পদস্থ পুলিশ কর্মচারী এবং কবি কুলচন্দ্র দে এবং মা পূর্ণ শশী।তার তখন মাত্র ৪ বছর বয়স,তখন তাঁর বাবা মারা যান।
তাঁর দাদা সরকারি আর্ট কলেজ চারু ও কারু মহাবিদ্যালয় এর প্রথম অধ্যক্ষ মুকুল দে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। সেই সময়ে রানী থাকতেন দাদার সাথে। কলকাতাতেই চৌরঙ্গীতে সরকারি আর্ট কলেজের কোয়ার্টারে। সেখানে প্রায়ই আসতেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখা রানীর।
১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এবং তাঁর বোন অন্নপূর্ণাকে (ঘোষ) শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি করে দেন এবং খুব কম সময়েই তিনি নন্দলাল বসুর প্রিয় ছাত্রী হয়ে ওঠেন। পরে তিনি অবনীন্দ্রনাথের কাছেও আঁকা শিখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তিনি যৌথভাবে বাল্মিকী প্রতিভা নাটকের সিরিজ এবং শান্তিনিকেতনের দৃশ্যাবলির রঙিন ছবি আঁকেন।তাঁর আঁকা ছবিগুলোর ভিতর রাধার বিরহ এবং ১৯৩০ সালে লিনোকাটের উপর তাঁর একটা বই খুব প্রশংসা পেয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনি জড়িয়ে পড়েন স্বাধীনতা সংগ্রামে (আগস্ট আন্দোলন), ধরাও পড়েছেন এবং জেলও খেটেছেন।
১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে দেশের প্রথম মহিলা চিত্রশিল্পী হিসেবে দিল্লিতে চিত্রপ্রদর্শনী করে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর আঁকা ছবি দিয়ে তৈরি অ্যালবাম খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর আঁকা ছবিগুলি দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন সহ বিভিন্ন রাজ্যের রাজ ভবনগুলোতেও স্থান পেয়েছে। চীনের প্রধানমন্ত্রী চুনকিং ভারতে এলে ভারত সরকার রানী চন্দের আঁকা ছবি সৌহার্দ্যের প্রতীক হিসেবে চীন সরকারের হাতে তুলে দেয়।
তিনি সঙ্গীত এবং অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠান করেছেন তখন তিনি সেই সব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রীলঙ্কায় মঞ্চস্থ 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যে তিনি নাচে অংশ নিয়েছিলেন।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর স্বামী ভোটে জিতে নেহেরুর মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী হওয়ার(১৯৫২) তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে স্বামীর সাথে দীর্ঘ কুড়ি বছর দিল্লিতে ছিলেন। জহরলাল নেহেরুর, বিজয় লক্ষী পন্ডিত প্রমুখের সাহচর্য আসেন।
১৯৫৫ সালে তিনি স্বামীর সাথে সাংস্কৃতিক দলের অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে পূর্ব ইউরোপ এবং তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণ করেন।
রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা এবং নির্দেশে তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যায় যখন কবি একটানা লিখতে পারতেন না তিনি গুরুদেবের মুখে মুখে বলা রচনার অনুলিপিকার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা 'মৃত্যু'( দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে/ এসেছে আমার দ্বারে) লিপিবদ্ধ করেছেন এই নারী।
এছাড়া অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী এবং তাঁর দুটি দুটি স্মৃতিকথা 'জোড়াসাঁকোর ধারে' এবং 'ঘরোয়া' তাঁরই অনুলিখন।১৯৫৪ সালে 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পান। সাহিত্যকীর্তির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করে।
তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর ১৯৭২ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন এবং তিনি সেখানেই আমৃত্যু কাটান।তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৯৭ সালে।
* তথ্যসংগ্রহ- দেবব্রত সরকার

লেখিকা পরিচিতি
সুমনা সরকার, রবীন্দ্রমেলার সদস্যা।

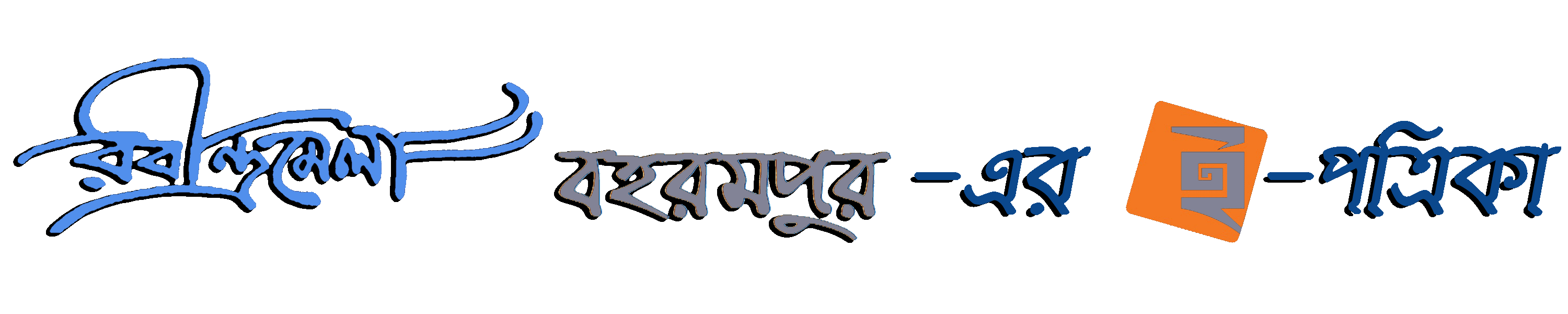
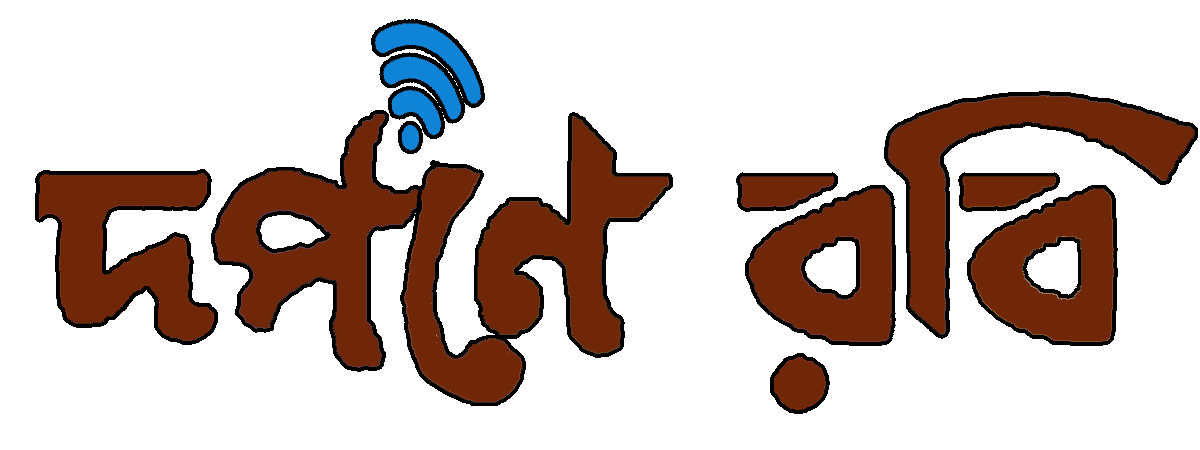



Comments