রবীন্দ্রনাথ/বাংলা নাটক/আমাদের ভবিতব্য
- Jan 31, 2021
- 6 min read
কুমার রায়

শেক্সপীয়ার ও রবীন্দ্রনাথের নাট্যভবিতব্য বোধ করি দুটি স্বতন্ত্র রাশিচক্রের অবদান। দুজনেই কবি, দুজনেই নাট্যকার। মিল শুধু এইটুকুই। কিন্তু নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য শেক্সপীয়ারের নাট্যভাগ্য থেকে আলাদা। শেক্সপীয়ারের নাটক লিখিত হবার পর অভিনীত হয়েছে, ছাপা হয় নি। রবীন্দ্রনাথের নাটক লিখিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হয়েছে- কিন্তু অভিনীত হয় নি(তাঁর পারিবারিক এবং শান্তিনিকেতনের মঞ্চ ছাড়া)। ছাপার ফলে তাত্তবিক আলোচনা শুরু হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা। ফলে মঞ্চের সঙ্গে আড়ি পাতা হয়ে গেল। ভক্তি গেল বেড়ে।
রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা ও রাণী’ নাটকের ত্রিবেদী এক দৃশ্যে বলেঃ “ কেন, আমার কি বেদের ওপর কম ভক্তি? আমি বেদ পুজো করি, তাই পাঠ করার সুবিধে হয়ে ওঠে না। চন্দনে আর সিঁদুরে আমার বেদের একটা অক্ষরও দেখবার জো নেই।”-
রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে দীর্ঘকাল আমাদের ওই ত্রিবেদীর দশা চলছিল। বেদের মতোই পুজ করেছি- চন্দনে আর সিঁদুরে লেপা কাব্য করে আমরা তার অভিনয়যোগ্যতা সম্পর্ক অন্ধ থেকেছি। অভিনয় করা হয়ে ওঠে নি। কেবল নাট্য আন্দোলনের যে ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত সেই সময়েই একটা পর্বে রবীন্দ্র নাটক যে অভিনয়যোগ্য অসাধারণ আধুনিক নাটক এ চেতনা প্রখর হয়েছিল।
অথচ আগে অনুভব হয়নি কেন- বা ঠিক এই বর্তমানে হচ্ছে না কেন-এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠবে। কারণগুলো এইভাবে দেখা যেতে পারে।
একঃ বনিয়াদ তৈরির আগে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমশঃ অর্থনৈতিক কারণে জনরূচির কাছে আত্মদান। মাইকেল, দীনবন্ধুর শুরুটা ব্রিলিয়ান্ট সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা অনুসৃত হয় নি।
দুইঃ বাংলা নাটক একচক্ষু হরিণের মতো চারণভূমিতে বিচরণ করতে লাগল। ঘটনার ধাপে ধাপে আরোহ, অবরোহ, চমক, বাকবাহুল্য ইত্যাদি ছিল মঞ্চ সফল নাটকের প্রধান সম্বল। বাইরের দিকে নিবদ্ধ নেত্র তার। অভিনেতা-সম্বল। নাট্যকারের থিয়েটার নয়। হ্যাঁ, গিরিশচন্দ্রকে স্মরণে রেখেই বলছি। মঞ্চের সঙ্গে ‘প্লে’র সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য হ’ল- ড্রামা রইল দূরের বস্তু।
তিনঃ রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন সময়ের আগে এবং নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় রহিত রয়ে গেলেন।গিরিশচন্দ্রের পর আর সকলে, একাদিক্রমে ও একই প্রয়োজনে, তাঁরই কায়দাকানুন মেনে উল্টে পাল্টে নানাভাবে, ভঙ্গীতে – চালাতে চেয়েছেন। একটিমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। দীর্ঘদিনের ঐকান্তিক সাধনায় তিনি একটি নতুন রূপের উদ্ভাবন করলেন।
চারঃ রবীন্দ্রনাথের নাটক লেখবার পর শেক্সপীয়ারের নাটকের মত অভিনীত হ’ল না রঙ্গালয়ে, কিন্তু তাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। শেক্সপীয়ার বা ইবসেন, চেখভ, স্ট্রীণ্ডবার্গ অথবা সার্ত্র, কাম্যু, ইওনেসকো- এদের নাটকের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক আলোচনাটা শুরু হয়েছে নাটক অভিনীত হবার পরে। শেক্সপীয়ারের ক্ষেত্রে তো এ্যাকাডেমিক আলোচনা শুরু হয়েছে অনেক পরে। হ্যামলেট অভিনীত হয়েছে কতশত বার কত শত ভাবে। তারপর একদিন চার্লস স্ল্যাম ফতোয়া দিয়েছেন এ নাটক অভিনয়ের জন্য- নির্জন পাঠ গৃহে একাকী রসাস্বাদনের বস্তু। তাতে অবশ্য হ্যামলেটের অভিনয় বন্ধ হয়নি -আজও কতভাবে তা হচ্ছে। নাটকের আস্বাদন মঞ্চে- প্রত্যক্ষণের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ অভিনীত হল না। (তাঁর পারিবারিক মঞ্চের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র) কিন্তু জ্ঞানীগুণীরা তাত্ত্বিক আলোচনা শুরু করে দিলেন।যাঁরা যে দায়িত্ব নিলেন মঞ্চের সঙ্গে, নাট্য শিল্পের সঙ্গে তাদের কজনের সম্পর্ক কতখানি তা অবশ্য অনুসন্ধানের বিষয়।চার্লস ল্যামের মত রবীন্দ্রনাথের নাটকের কাব্যগুণ, সাহিত্যগুণ, জীবনদেবতা, আধ্যাত্মবাদ, রোমান্টিসিজম, লিরিকধর্মীতা বিচার করে বড়ো জোর মেটারলিঙ্কে সঙ্গে একটা তুলনা করে তাদের কর্তব্যকর্ম শেষ করলেন এবং াট্য বিচারের মানদণ্ড তাদের হাতে যা ছিল তা ওই ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজী শিক্ষার ফলে ইউরোপীয় বা বলা ভালো এলিজাবেথীয়। রবীন্দ্রনাথের নতুন রূপ সে নিরিখে অভিনয়যোগ্য নাটকের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হ'ল না। আমরাও ওই ত্রিবেদীর মত ভক্তিভরে সিঁদূর চন্দন লেপে তাকে তুলে রাখলাম।
শেক্সপিয়ার তো থিয়েটারেরই মানুষ ছিলেন এবং ইউরোপের যেসব নাট্যকার প্রচলিত পথ ছেড়ে নতুন রূপ নাটকে খুঁজেছেন তাঁদের সৌভাগ্য যে তাঁর থিয়েটার পেয়েছিলেন এবং সেই নতুন রূপকে সেই থিয়েটারের মধ্যে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছেন এবং এক একটা আন্দোলনের সূচনা করেছেন। এমনকি গ্যয়টের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের নৈকট্যের কথা বলা হয়ে থাকে তিনিও ভাইমারের থিয়েটার পেয়েছিলেন-‘ফাউস্ট’ অভিনীত হয়েছিল।
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাট্য ভাবনার সঙ্গে কেউ সক্রিয়ভাবে থিয়েটারের কাজে যুক্ত হলেন না। আর একভাবে আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যায়-চেখভের নতুন নাট্যশৈলীর মঞ্চ রূপে নতুন অভিনয় ধারার কথা ভাবতে হ’ল এবং ভাবনাকে কাজে রূপান্তরিত করতে হ’ল; আঁতোয়ান স্বভাববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে মঞ্চের চেহারাটাই পাল্টে দিলেনঃ পিরানদোল্লার বিকলনধর্মী নাটকের প্রয়োজনে মঞ্চকে ভাঙতে হলো; আমেরিকার ইউজিন ওনীল ‘দ্য এম্পারার জোনস’-এর মত নাটক লিখলেন। আর একেবারে আধুনিক কালে ব্রেখট তাঁর নতুন নাট্যাদর্শকে সাধারণের সামনে তুলে ধরতে ‘এপিক থিয়েটার’ বার্লিনার আঁসেম্বল করলেন। একটা আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন।
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এরকম কোন চেষ্টাই হলো না। জানি রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র নাট্যকার নন-তাঁর প্রতিভা সর্বব্যাপী। কিন্তু নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে চিনে নেওয়ার- তাঁর নাটক নিয়ে পরীক্ষা করবার দায়িত্ব ছিল থিয়েটারের মানুষদের, মঞ্চের মানুষদের। শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরীর আমলে একবার বিচ্ছিন্ন চেষ্টা হয়েছিল মাত্র। কিন্তু সেই চেষ্টা ‘আকাশের কলহংস’কে পানা পুকুরে আবদ্ধ করবার চেষ্টা মাত্র। অনেকের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলতে ভরসা পাচ্ছি একটিমাত্র বিশ্লেষণের সূত্রে।প্রয়োজন ছিল স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা-প্রয়োজন ছিল একটি পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করাঃ প্রয়োজন ছিল মজে যাওয়া দর্শকদের কিছুটা আঘাত দিয়ে সচেতন করে দেওয়া(‘নাচ ঘরের প্রচেষ্টা সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করছি এ প্রসঙ্গে, কিন্তু সেটা একটা বিরল ব্যতিক্রম)রবীন্দ্র নাটক নিয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা। কোনটাই হয়নি।
এগুলো অভিযোগ আকারে পেশ করছি নাঃউল্লেখ করছি ঘটনা হিসেবে। তখনকার থিয়েটারের বাস্তব অবস্থাটা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নাট্য প্রতিভা প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না একথা মানতেই হবে। অভিনেতাদের সুবিধার জন্য মাপসই ভূমিকা নেই, দর্শকদের খুশির জন্য প্রস্তাবনা, নাচ-গান, ডুয়েট সং সঙ্গী্ সংগ্রাম, ম্যাডসীন ডাইং স্পীচ, উজ্জল দৃশ্য কোনোটাই রবীন্দ্রনাটকে নেই।স্থুলতর প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করবার মশলা নেই, পাত্রপাত্রীর বক্তৃতার চেয়ে ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ, সমাধানের চেয়ে সংকেতকে তিনি বড়ো করেছেন, উত্তেজনার চেয়ে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে আন্দোলিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু সে সময়ের থিয়েটারের ইকনমিক্স এবং জনরুচির দরবারে এতোগুলো ‘নেই’কে নিয়ে আসর জমানো মুশকিল ছিল।
৩৫ বছর আগে থিয়েটার নিয়ে একটা নতুন ভাবনা শুরু হ’ল। সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে। এই তিন দশকের থিয়েটারটাও খতিয়ে দেখতে হবে। গ্রুপ থিয়েটার আজ আমাদের গর্বের বস্তু। মননে চিন্তায় আধুনিক হবার প্রচেষ্টা সর্বত্র। প্রত্যেক আন্দোলনের দু’টো দিক থাকে, এক উত্তেজনার দিক আর এক সংগঠনের দিক। আন্দোলনে উত্তেজনা থাকা স্বাভাবিক প্রাথমিক পর্বে। উত্তেজনা ভাঙে, উত্তেজনা অনেক মানুষ্কে একত্রিত করে। কিন্তু অভীষ্ট ফল লাভ হয় সংগঠিত পর্বে। নাট্য আন্দলনে আমরা আজও ওই উত্তেজনার কালটা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। শিল্পের সামাজিক দায়িত্ব শিল্প আন্দোলনের সাংগঠনিক পর্বেই সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হওয়ার কথা- কেননা শিল্পের সে দায়িত্ব পালন করবার যোগ্যতা অর্জন তখনই সম্ভব যখন উত্তেজনা পর্ব শেষ হয়ে গিয়ে শিল্পের কর্মীরা শীতল নির্ভীক্ষু দৃষ্টি লাভ করবে, পারম্পর্য বুঝতে পারবে এবং শিল্প গভীর কথা বলতে পারবে সহজ করে।আত্মপরিচয় লাভ করতে হবে, শিল্পকে মেলাতে হবে দেশের প্রাণের সঙ্গে, জারি অবচেতন স্তর থেকে খুঁজে আনতে হবে আবেগ আর অনুভূতি গুলোকে। এটাই শিল্পের মাধ্যমে রিয়েলিটি খোঁজা। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে এই রিয়েলিটি বুঝতে চেষ্টা করে-শিল্পীও তাই করে। এইসব কথা এক আধজন মানুষ অবশ্যই ভেবেছেন- কারণ তখন সেই মুষ্টিমেয় মানুষগুলি আন্দোলনের সংগঠনের কথা ভেবেছেন-ভেবেছেন যে উত্তেজনা পর্ব থিতিয়ে এই শিল্পকে গভীর রূপে প্রকাশ করতে হবে। এই ভাবনা থেকেই রবীন্দ্র নাটক আধুনিক মঞ্চে রূপ পেল।
১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৫৪ এবং এক দশকের শেষে এসে মনে হলো এবারে বোধহয় বাংলা থিয়েটার সাবালক হলো-সংঘটিত হলো। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত হ'ল। কেননা ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৪ সালে শুধু 'রক্তকরবী' নয় 'ডাকঘর, 'মুক্তধারা', বিসর্জন', 'রাজা' অভিনীত হ'ল।তার আগেই ১৯৫১ সালে 'চার অধ্যায়' অভিনীত হয়েছে এবং সেই সূত্রপাত রবীন্দ্র কাহিনী নিয়ে পরীক্ষা আধুনিক থিয়েটারে। 'অচলায়তন হয়েছে, কালের যাত্রা' অভিনীত হয়েছে।কিন্তু এই সচেতন প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত হয়ে নয়। বরং বলা ভালো রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করে বাংলা থিয়েটার যতখানি এগিয়ে যেতে পারতো এবং বিশ্ব থিয়েটারের আসরে একটা নতুন ধারার উদ্ভব এই বাংলাদেশ থেকে ঘটিয়ে দিতে পারতো-তা অন্য খাতে বইতে থাকল।একসময় কিছু লোকের মনে হ'ল এসব ভাববাদী তামাশা মানুষকে সংগ্রাম বিমুখ করবার ছল মাত্র। আমরা 'নাটকের যুগে' নিজেদের উত্তীর্ণ না করে 'নাটকে যুগে' নিজেদের মেলে ধরেছি। তারই ফলে এ যুগেও একটি মাত্র দল ছাড়া রবীন্দ্র নাটক আর কেউ করলেন না। ক্ষনণিকের ক্রোধ, ক্ষণিকের উদ্দীপনায় অনেক সহজে হাততালি পাওয়া যায় যে।রিয়ালিটির গভীরের অন্বেষা, মানুষের জীবনের অতলান্ত সীমানা আবিষ্কারের সঙ্গে রবীন্দ্র নাট্যচর্চা যুক্ত হলো একটি মাত্র সংস্থায়, আর অপরদিকে সহজ সাফল্যের আকর্ষণ, বিদেশের নাট্যচর্চার নতুন সংবাদে আমাদের উৎসাহ এবং জীবনের আচার-আচরণ, পোশাক, ফ্যাসান ইত্যাদির মতো বিদেশের অনুকরণে আমাদের অন্ধ আগ্রহ নাট্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে পাশে ফেলে রাখলো।
ঠিক এক্ষুনি বাংলা থিয়েটারে ব্রেখটকে নিয়ে প্রচুর উৎসাহ। ব্রেখটের একটি নাটক আজ তিনটি দল সমারোহে করছেন কলকাতার মঞ্চে। রবীন্দ্রনাথের কোনও নাটক নিয়ে এরকমটি হ'ল না-হয়নি। কেন? রবীন্দ্রনাথ কঠিন বলে কিংবা রবীন্দ্রনাথ আধুনিক নন বলে? উত্তর টা কে কি বলবেন জানিনা-আমাকে জিজ্ঞাসা করলে প্রথমটির উত্তর হবে রবীন্দ্র নাটকের প্রযোজনা সত্যিই কঠিন এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর- না । রবীন্দ্রনাথ আধুনিক, প্রচন্ডভাবেই আধুনিক আজও, এখনও পর্যন্ত। রবীন্দ্র নাটক আধুনিক এবং মহৎ তাই তা ক্লাসিক পর্যায়ে উন্নীত হবার যোগ্য। যেমন শেক্সপিয়ারের নাটক মহত এবং ক্লাসিক, যেমন শিলার, গ্যয়টে।একাধিক দল বিভিন্নভাবে আজও শেক্সপিয়ারের নাটক অভিনয় করছেন তার দেশেই-একই নাটকে কতভাবে গুণী অভিনেতা ও পরিচালকের সমাবেশ ঘটে প্রতিবছর স্ট্রাটফোর্ড-অন-এভন-এ। জার্মানিতে সারাবছর অভিনীত হচ্ছে শিলার এবং গ্যয়টে এবং আধুনিক নাটক্যার ব্রেখট।সেখানে ১৯৫৭ সালের একটা হিসেব দেখতে পাচ্ছি শিলার-২০০০ বার, গ্যয়টে ১২০০ বার এবং ব্রেখট ১১২০ বার অভিনীত হয়েছে। এই অংকগুলো এবং ঘটনাগুলো কি আমাদের একটু ভাবাবে নতুন করে-নাকি সব ভাবনা রবীন্দ্র নাটক নিয়ে ভেবে শেষ করে ফেলেছেন শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র এবং তার দল বহুরূপী? আর নতুন করে রবীন্দ্র নাটক নিয়ে ভাববার বা চর্চা করবার কোনও তাগিদ অনুভব করছি না আমরা।
আমাদের নিজেদের পরিচয় জানবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই রবীন্দ্র নাটক করা।আমাদের আকাঙ্ক্ষা যদি হয় নিজেদের জেনে বাস্তবকে মেনে নিয়ে- একটা গভীর ছন্দে উপনীত হওয়া তা'হলে রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করতেই হবে। জানি রবীন্দ্রনাথই শেষ কথা নয়। তবু ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ রবীন্দ্রনাথ চর্চার মধ্যেই। আমাদের থিয়েটারের চেষ্টাটা যদি হয় ব্যক্তিগত মানুষের আত্মগত এবং বস্তুগত ভাবে আবিষ্কার করা তা'হলে রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই নতুন করে তা শুরু করতে হবে।রবীন্দ্র নাটক জটিল বাইরের জগত এবং ভেতরের জগতকে মিলিয়ে দিয়ে এখানে এক স্বতন্ত্র মূর্তি। প্রমাণ হয়ে গিয়েছে আধুনিক মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ কত নিশ্চিতভাবেই আধুনিক। সেই মঞ্চ সফল নাটকগুলির প্রযোজনার ইতিহাস, প্রযোজনার বাধা এবং তার থেকে উত্তরণ এসব কথা আলোচনা করা যেতে পারে।শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র রবীন্দ্র নাটকে কী আবিষ্কার করতে চেয়েছেন কিভাবে তিনি রবীন্দ্র নাটকের আধুনিক রূপটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন -তাও আলোচনা করা যেতে পারে। তবু আধুনিক থিয়েটারের দল মানুষকে রবীন্দ্র নাটকে মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে না। তার কারণ সংগঠনের পর্বটা স্থায়ী হল না, উত্তেজনার পর্বটাকেই আমরা জিইয়ে রেখেছি। মানুষকে মজিয়ে রাখতে চাইছি। থিয়েটারে উদ্বোধন চাইছি না।'সেনটিমেন্টাল', 'সেনসেশন্যাল' হয়েই থিয়েটার আবর্তিত হয়ে চলেছে। কখনো ধর্ম, কখনও স্বাদেশিকতা, কখনো রাজনৈতিকতা, কখনো আমদানি-আধুনিকতা এই মোড়কে সেন্টিমেন্টাল-সেনসেশন্যাল হওয়াই যেন থিয়েটারের অনিবার্য ভবিষ্যৎ।
বিঃদ্রঃ এই প্রবন্ধটি ১৩৮৮ সালের রবীন্দ্রমেলা স্মরণিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

লেখক পরিচিতি
কুমার রায়ঃ নাট্যকার সংগঠক গবেষক, বহুরূপীর সভাপতি, নাট্যনির্দেশক ও বহুরূপী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিয়াল্লিশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রেপ্তার বরণ করেন। তাঁর অভিনয়, নাট্য গবেষণা, নাট্য প্রযোজনায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় আছে।

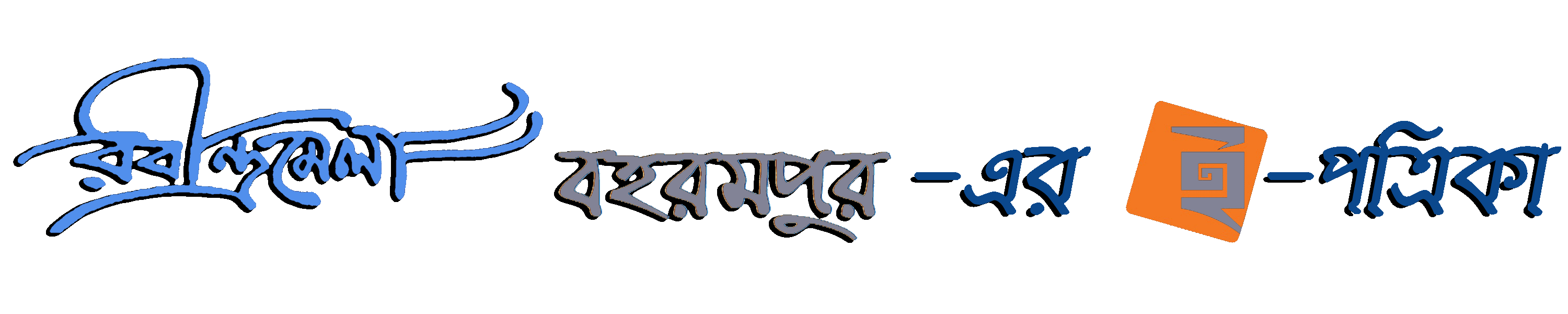
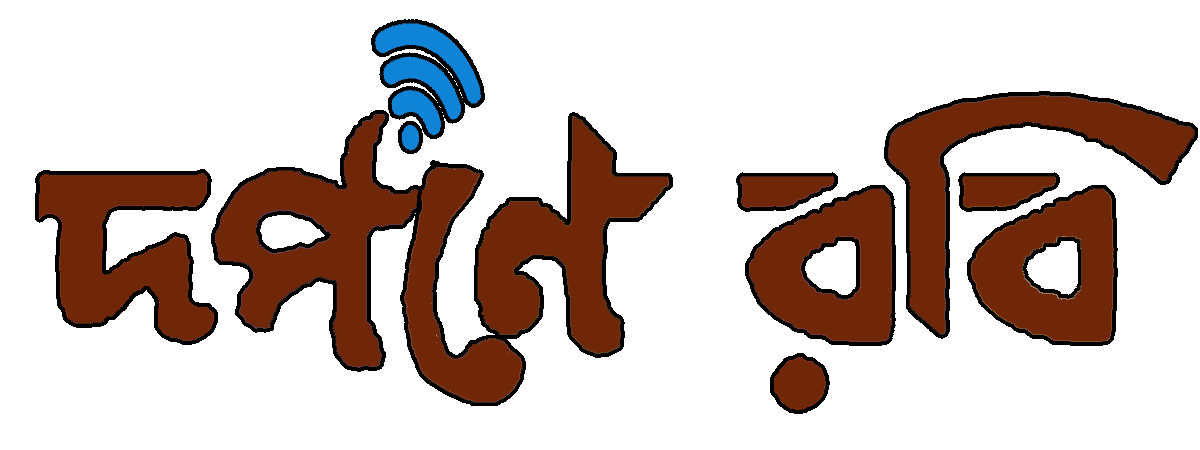







Comments