রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও ফ্যাসিবাদ
- Oct 22, 2020
- 4 min read
অনির্বাণ দাস

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছিলেন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে। ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতেই সারাজীবন নিজের সৃষ্টিকর্মে নিমগ্ন ছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাস্তায় নামলেও সেই সময়ে লিখিত কবিতা ও গানে কিন্তু সেভাবে সমকালীন রাজনৈতিক বিক্ষোভের প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায় না।যদিও তাঁর রচিত গান-কবিতায় দেশভক্তি কিছু কম নেই। অরবিন্দের বন্ধু হিসেবে রবীন্দ্রনাথও কিন্তু ব্রিটিশ রাজশক্তির কালো তালিকায় ছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলাদেশ উত্তাল। মানিকতলার বোমার মামলা এবং ক্ষুদিরামের ফাঁসি গোটা ভারতে আলোড়ন তুলল।কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তার প্রকাশ নেই।যদিও আন্দামানের কারাগারে বিপ্লবীদের চিঠি পাঠিয়েছিলেন, বাংলার ফুলকে না শুকোতে দেবার বাসনা নিয়ে, যে চিঠি ব্রিটিশ সরকার ৪৫ দিন গোপন রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন কবিতা হল নিত্যকালের অনুভবের ব্যঞ্জনা, নিছক ইতিহাসের ঘটনাবলী সেখানে স্থান করে নিতে পারে না।আর সে কারণেই সমকালীন ব্যক্তিনামকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় সেভাবে আনেন নি।তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, সে কথা বারান্তরে।
তবে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। এ যুদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে সত্যিই বিচলিত করেছিল।এই সময়ই যখন ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটল, তার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করলেন। কবির ভাবনায় এল আমূল পরিবর্তন।
১৯১৪ সালে রাশিয়া-ফ্রান্স-জার্মানি-অস্ট্রিয়া-ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধের আবহে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের আশ্রম মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনার দিন এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি দিলেন—
“সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল! অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। ...মানুষের এই-যে প্রচণ্ড শক্তি এ বিধাতার দান। তিনি মানুষকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েছেন এবং দিয়ে বলে দিয়েছেন, যদি তুমি একে কল্যাণের পক্ষে ব্যবহার কর তবেই ভালো, আর যদি পাপের পক্ষে ব্যবহার কর তবে এ ব্রহ্মাস্ত্র তোমার নিজের বুকেই বাজবে। আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন করবার জন্য নিজের এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহার করেছে; তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারই বুকে বেজেছে। মানুষের বক্ষ বিদীর্ণ করে আজ রক্তের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে চলবে-- আজ কে মানুষকে বাঁচাবে! এই পাপ এই হিংসা মানুষকে আজ কী প্রচণ্ড মার মারবে-- তাকে এর মার থেকে কে বাঁচাবে!”
(পরে এই ভাষণটি ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যায় ‘মা মা হিংসীঃ’ শিরোনামে মুদ্রিত হয়।)
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখতেন রবীন্দ্রনাথ। যুদ্ধ-নিরপেক্ষ বেলজিয়াম-এ অনৈতিকভাবে জার্মান অনুপ্রবেশ কবিকে নাড়া দিয়েছিল।তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন—“বেলজিয়ামের কীর্ত্তি মনে খুব লেগেছে—সেদিন ছেলেদের এই নিয়ে কিছু বলেছিলুম—হয়ত দেখবে কবিতাও একটা বেরিয়ে যেতে পারে”। চিঠিপত্র ৫, পত্রসংখ্যা ৩১
সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে কবিতায় নিয়ে আসার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত কিছুটা পরিবর্তিত হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর; পরে আরও কিছুটা পরিবর্তিত হল আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ফ্যাসিবাদী শাসনের নিষ্ঠুরতার প্রতিক্রিয়ায়। যুদ্ধবাজ স্পেন, ইতালি, জাপান ও জার্মানির প্রায় প্রতিটি ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনকে ধিক্কার ও ক্ষোভ জানিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন, কলম ধরেছেন। জাপানের চীন আক্রমণ তাঁকে ব্যথিত করেছিল।তিনি লিখেছেন -
‘জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ-মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে; ভক্তির বাণ বুদ্ধকে’।বুদ্ধভক্তি
সমকালের ফ্যাসিবাদী অস্ত্রে বিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ জাপানের চীন আক্রমণ নিয়ে ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে লিখলেন-
“যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে,
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়”। পত্রপুট-১৮
তার পরে পরেই ১৯৩৮ এর জানুয়ারিতে লিখলেন ‘বুদ্ধভক্তি’-
“হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির--
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।” নবজাতক
১৯৩৭ এ লিখলেন ‘আফ্রিকা’ – পটভূমি কিন্তু ইতালির ইথিওপিয়া আক্রমণকে কেন্দ্র করেই। সমকালের ছাপ সে কবিতায় আছে বটে তবে মূলত বিগত দিনে আফ্রিকাতে যে অত্যাচার ও শোষণ চলেছিল সেটাই এই কবিতার উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথ শোষকের প্রতি ‘মানহারা মানবী'–র কাছে ক্ষমা চাইবার যে আহ্বান জানিয়েছেন—সেই সচেতনতা অবশ্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কালে জাগরিত হয়েছিল।
১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারি মাস, কবি লিখছেন ‘ছড়া’ সংকলনের ‘শ্রাদ্ধ’ কবিতাটি।এই কবিতায় একটি গ্রাম্য জীবনযাত্রাকে মসৃণভাবে বর্ণনা করে চলেছেন খুবই অনায়াস ও আটপৌরে চালে। কিন্তু প্রতিটি স্তবকের শেষে চার পঙ্ক্তির একটি করে ছোটো স্তবক যার প্রধান চরিত্র হল রেডিও—যে-রেডিও প্রতিমুহূর্তে বয়ে নিয়ে আসে মৃত্যুর বিভীষিকা। সেখানে কবি বলছেন-
"ঐ শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি;
দেশবিদেশে শহরগ্রামে গলা-কাটার ধুম কী।” ছড়া-৬
সচেতন পাঠক নিশ্চয় বুঝবেন ইতিহাসে বোঁচা গোঁফের প্রতীকী তাৎপর্য।
সেখানে কবি আরও লিখেছেন-
“গ্যাঁগোঁ করে রেডিয়োটা কে জানে কার জিত--
মেশিন্গানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।”
রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় খুব কম ক্ষেত্রেই ইতিহাসের ব্যক্তিনাম ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর অনীহা ছিল কিন্তু তবুও কিছু মুহূর্তে সমকালীন ঐতিহাসিক ক্ষমতালুব্ধ শাসককে পাঠকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি।
১৯৪০-এর ৩১ মে কবি লিখলেন-
“দামামা ঐ বাজে,
দিন-বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।”জন্মদিন-১৬
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। কবি তখন অসুস্থ শরীর নিয়ে কালিম্পং–এ। ১৯৩৯-এ ফিনল্যান্ড রাজি হয়নি নিজেদের জমি ছাড়তে। কিন্তু পরাক্রমী রাশিয়ার আগ্রাসনে ফিনল্যান্ড ১৯৪০-এর ১২ই মার্চ মস্কো শান্তি চুক্তি বাধ্য হল।আর ১৯৪০-এর মে মাসে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘অপঘাত’ নামে একটি কবিতা।পল্লীগ্রামের রূপ বর্ণনা করতে করতে কবিতাটি সহসা শেষ হয়ে যায় –
‘টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিন্ল্যান্ড্ চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।‘ সানাই
রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমকালীন রাষ্ট্রনীতির আন্তর্জাতিক স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছে খোলাখুলি ভাবে। ‘সভ্যতার সংকট’ বলে যাকে মনে করেছেন তাকেই তুলে এনেছেন কবিতার আঙ্গিকে। জাপানের হাতে ১৯৩৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর নানকিং শহরের পতন ঘটে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে জাপানি সৈন্য। এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে ২৫ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন-
'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।' প্রান্তিক-১৮
১৯৪১ সালে কবির অস্ত্রোপচার হবে।শুরুর কিছুক্ষণ আগেও কবিগুরু উৎকণ্ঠিত হয়ে যুদ্ধের খবর জানতে চাইলে, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আশ্বাস দিলেন যে, রুশ রণাঙ্গনে নাৎসি বাহিনীকে কিছুটা বোধহয় ঠেকানো গেছে। শুনে রবি ঠাকুরের শেষ কথা ছিল – ‘পারবে, ওরাই পারবে’।
এই সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বর্শা-ফলকে বিদ্ধ মানবতার কবি গর্জে উঠেছিলেন বারে বারেই। তাই তো কবি কন্ঠে ধ্বনিত হয়েছে-
‘মহাকালসিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন...’ প্রান্তিক-১৭

লেখক পরিচিতি
অনির্বাণ দাস, রবীন্দ্রমেলার সদস্য

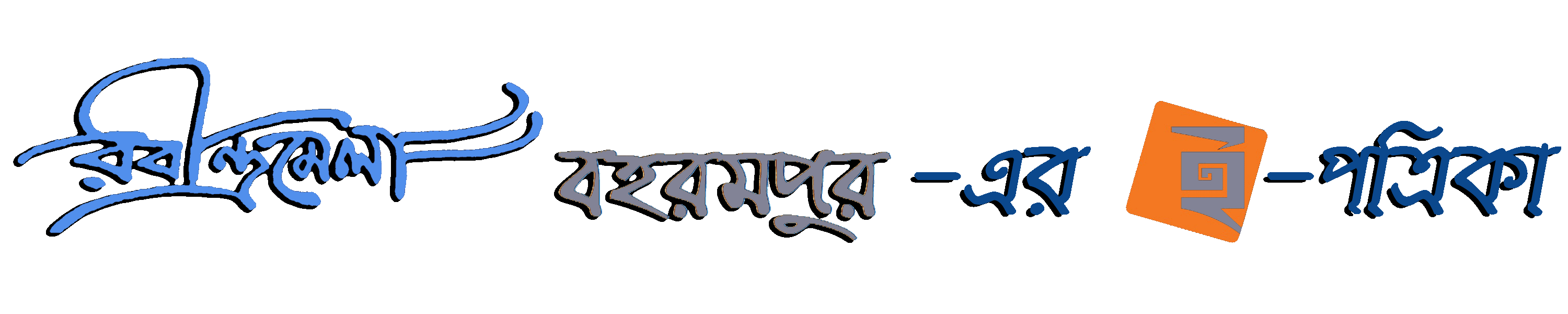
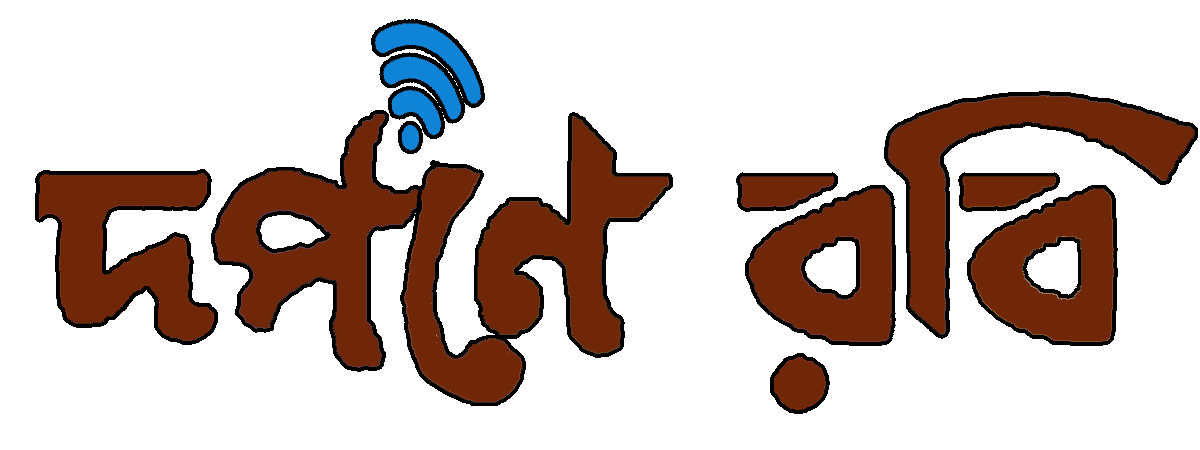







Comments