রবীন্দ্রনাথের সমবায় ভাবনা
- Aug 8, 2021
- 3 min read
শ্রীমন্ত ভদ্র

বিশ শতকের গোড়ায় ইউরোপের সমবায় আন্দোলন শুরু হয় প্রথমে ইংল্যান্ড ও পরে ফ্রান্সে এবং অনান্য দেশে। আয়ারল্যান্ডের সমবায় আন্দোলনের জনক স্যার হোরেস প্লাঙ্কেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানী জর্জ উইলিয়াম রাসেলের লেখা "national being ' বইটির মাধ্যমে।এরপরেই ভারতে সমবায় নীতি প্রবর্তনে সচেষ্ট হন রবীন্দ্রনাথ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই স্বদেশী দ্রব্য তৈরি ও বিক্রয় এর ভান্ডার তৈরি করেন এবং ভান্ডার নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন।
মানবপ্রেমিক কবি সমবায়ের মাধ্যমেই খুঁজে পেয়েছিলেন মানুষের মুক্তির পথ।
সমবায়ের যে মূল সুর অর্থাৎ দশজনে একসঙ্গে থেকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা , তাই পরিস্কার করে বলেছেন তাঁর লেখায় -
"তোমরা যে পঞ্চাশ জনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক পৃথক চাষ করিয়া আসিতেছ, তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল-গোলাঘর পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরীব হইয়াও বড় মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে ।তখন কল আনাইয়া লওয়া ,কলে কাজ করা কিছুই কঠিন হইবে না ।কোন চাষীর গোয়ালে যদি তার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত একমাত্র দুধ বাড়তে থাকে, সে দুধ লইয়া সে ব্যবসা করিতে পারে না ।কিন্তু একশ দেড়শ চাষী আপন বাড়তি দুধ একত্র করিলে মাখন তোলা কল আনাইয়া ঘীয়ের ব্যবসা চালাইতে পারে ।ইউরোপে এই প্রণালীর ব্যবসা অনেক জায়গায় চলিতেছে ।ডেনমার্ক প্রভৃতি ছোটো ছোটো দেশে সাধারন লোকে এইরূপ জোট বাঁধিয়া মাখন-পনির-ক্ষীর প্রভৃতির ব্যবসা খুলিয়া দেশ হইতে দারিদ্র একেবারে দূর করিয়া দিয়েছে ।এই সকল ব্যবসায়ের যোগে সেখানকার সামান্য চাষী ও সামান্য গোয়ালা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আপন বৃহৎ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছে "
এত সহজ করে সমবায়ের মূল সুরের ব্যাখ্যা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্ব আর কেউ বলতে পারেন নি।
কবি জন্মেছিলেন জমিদারি পরিবারে। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি জমির মালিকানা পেয়েছিলেন এবং তার জমিদারির কাজে প্রজাদের হিতার্থে তিনি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করেছিলেন। উন্নয়নের কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে সামিল করেছিলেন প্রজাদেরও । যৌবনকালে রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের দারিদ্র,অনাহারক্লিষ্ট চেহারা দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন-
" ভারতবর্ষের মতো কৃষিনির্ভর দেশে কৃষির উন্নতি ব্যতিত কৃষকদের বাঁচানো যাবে না ।এই সঙ্গে চাই কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠা।সমবায় নীতি প্রচলন ছাড়া ধনী নির্ধনের সংঘাতের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় ।"
মহাজনী ঋণের চড়া সুদের হাত থেকে তার জমিদারীর প্রজাদের রক্ষা করতে বন্ধু-বান্ধব ও ধনী মহাজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে ১৯০৫ সালে পাতিসারে তৈরি করেন কৃষি ব্যাংক ।পরবর্তীকালে তার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এক লক্ষ আট হাজার টাকা শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে রাখা হল এই ব্যাঙ্কে। কৃষি ব্যাংক থেকে সুলভে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা হওয়ায় ওই অঞ্চলের মহাজনেরা মহাজনী ব্যবসা গুটিয়ে তাদের মূলধনও কৃষি ব্যাংকে জমা রাখতে বাধ্য হয়েছিল।
পরবর্তীতে শ্রীনিকেতনে আরো সংগঠিতভাবে সমবায় নীতি প্রয়োগ করে এলাকার চাষীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করেন রবীন্দ্রনাথ। কবির মতে সমবায়ের মূল কথা "কর্মশক্তিকে মিলিত করে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্য লাভ করা।" কবির চিন্তায় সমবায় একাধারে একটি পদ্ধতি অন্যদিকে সমাজ গড়ারও এক উৎকৃষ্টতর উপায় । বিশেষ করে সম্পত্তির ভাগ ও ভোগ নিয়ে যে সমস্যা সমাজে ঘটে তার সমাধানে এটি একটি মাঝামাঝি পথ হিসেবে গণ্য করা যায় বলে কবি মত প্রকাশ করেছিলেন।
তাঁর মতে "ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যতাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে যে উদ্বৃত্ব ঘটবে তা সর্বসাধারণের মধ্যে যদি বন্টন করা যায় তবে সম্পত্তি নিয়ে সমাজের যে দ্বন্দ্ব তার নিরসন ঘটে।"
১৯২৭ সালে ২২ শে নভেম্বর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক স্থাপিত হয়। ওই বছরই সমবায় ব্যাংকের পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সভ্যতার অগ্রগতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়ের মাধ্যমে পু্ঁজির সুষম বন্টন, সমাজতন্ত্রের ভাবনা সবটাই ধরা পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের সমবায়ের চিন্তায়।সমবায় শক্তির উপর প্রবল আস্থা রেখে 'সমবায়নীতি' তে তিনি লিখেছেন -
"আজ ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারত সভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে।ভারতবর্ষে আজ দারিদ্র্যই বহুবিস্তৃত, পুঞ্জধনের অভ্রভেদী জয়স্তম্ভ আজও দিকে দিকে স্বল্পধনের পথরোধ করে দাঁড়ায়। এইজন্য সমবায়নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই, আমাদের দেশে তার বাধাও অল্প ।তাই একান্ত মনে কামনা করি ধনের মুক্তি আমাদের দেশে সম্পূর্ণ হোক এবং এখানে সর্বজনের চেষ্টায় পবিত্র সম্মিলনতীর্থে অন্নপূর্ণার আসন ধ্রুবপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক।"
রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকার ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী করে এনে শ্রীনিকেতন গড়ে তোলার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। কুটির শিল্পে ব্যবস্থা করেন এব়ং এগুলি ক্রয়-বিক্রয়েও সমবায় নীতি অনুসরন করা হত । জমির আল ভেঙ্গে যৌথ কৃষি কর্মের জন্য লাঙ্গলের পরিবর্তে ট্রাক্টরের ব্যবহার শুরু হয়। হ্যামিলটন সাহেবের সমবায়ের সাফল্য কবিকে আরো বেশি করে সমবায়ে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহী করায় পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতনের এক সমবায় সম্মেলনে হ্যামিল্টন কে সভাপতি করে আনেন এব়ং নিজেও ১৯৩৫ সালে হ্যামিলটনের সমবায় সাফল্য ক্ষেত্র পরিদর্শন করেন।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাশিয়া যাওয়াকে তীর্থ দর্শন বলেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেছেন সারা দেশজুড়ে সমবেত কর্মের অনুষ্ঠান। ব্যক্তি এখানে তার আপন নিভৃত উদ্দেশ্য সাধন নিয়ে বসে নেই। সমাজের এই রূপটিই তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ছিল ।আবার ইউরোপ ভ্রমণের কালে সুইডেনের সাফল্যে সমবায়ের অবদান দেখে খুশি হয়েছিলেন ।সমবায়নীতির মূল কথা হল- কৃষিজীবী ও কারখানার শ্রমিক প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কাজ না করে একত্রিত হয়ে কাজ করবে। ফসল এবং উৎপাদিত দ্রব্যের লভ্যাংশের যথাযোগ্য ভাগ পাবে।
সেই যুগে একজন জমিদার হয়ে রবীন্দ্রনাথ সমাজের গভীরে প্রবেশ করে বুঝেছিলেন "কৃত্রিম উপায়ে ধন বন্টন করে কোন লাভ নেই ,সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই।জনসাধারণে যদি নিজের অর্জনশক্তিকে একত্রে মেলাবার উদ্যোগ করে তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে সকলের মধ্যে মূলধনের মূল্য তার ব্যক্তিবিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীম গুনে বেশি।"
"সকলের মিলিত কর্মশ্রমই আসল শক্তি"। তাই দূর্বলের শ্রমশক্তিকে একস্হানে জড়ো করে তাকে অর্থশক্তিতে রূপান্তর ঘটিয়ে রে অর্থশক্তি আসে সেটাই মূলধনের কাজ করে। বিশ্বকবির সমবায় ভাবনা এদেশের সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সকল মানুষের কাছে এক অমূল্য সম্পদ।

লেখক পরিচিতি
শ্রীমন্ত ভদ্র, রবীন্দ্রমেলার সদস্য

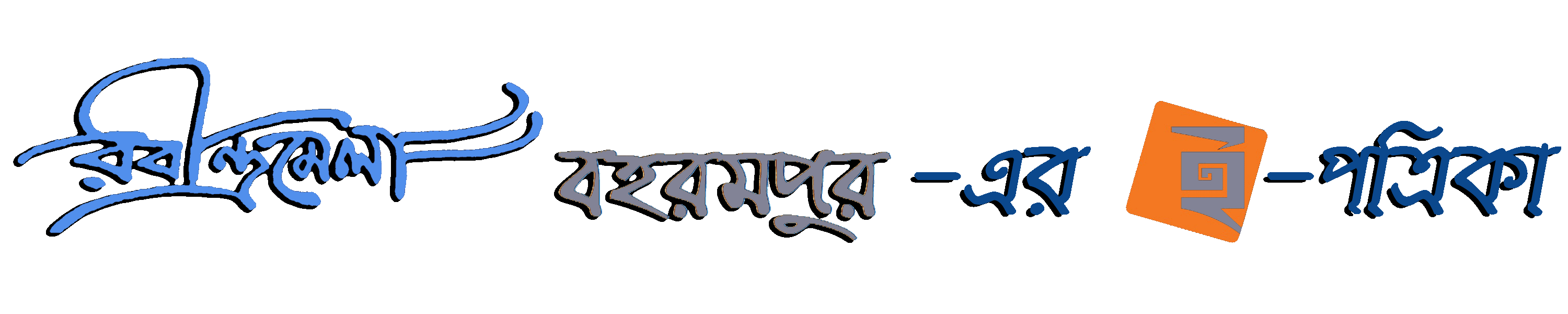
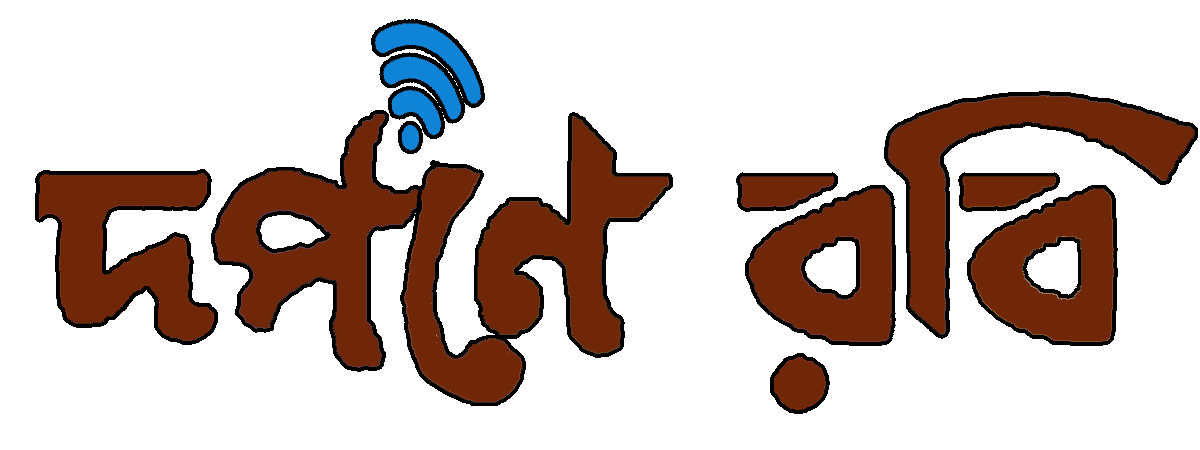



Comments