ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো
- Oct 11, 2021
- 4 min read
গার্গী মুখার্জী

সপ্তদশ শতাব্দী শেষ দিকে পঞ্চানন কুশারী তার কাকা শুকদেব কে নিয়ে যশোর থেকে এলেন কলকাতার গঙ্গার তীরবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে। এই পঞ্চানন কুশারী হলেন ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস সিদ্ধ আদি পুরুষ।
পঞ্চানন কুশারী ছিলেন বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। কলকাতায় এসে বসতি স্থাপন করলেন জেলেপাড়ায়। এই পাড়ায় ইতিপূর্বে কোন ব্রাহ্মণ ছিল না, এখানে পঞ্চানন পরিচিত হলেন ঠাকুরমশাই হিসেবে। (তবে পঞ্চানন জীবিকা নিয়ে দ্বিমত আছে, কেউ বলে তিনি জাহাজওয়ালাদের মাল সরবরাহ করতেন, কেউ বলে পুজো অর্চনাই ছিল তাঁর জীবিকা)। এপাড়ার লোকেদের মুখে পঞ্চানন কুশারী হলেন পঞ্চানন ঠাকুর। ইংরেজরা ও তাকে ঠাকুর বলেই ডাকতেন, শুধু উচ্চারণ বিকৃত হয়ে তা দাঁড়ালো টেগর। এরপর কুশারী পদবি উঠে গেল, তাঁরা নিজেরাও ঠাকুর পদবী ব্যবহার করতেন।
1707 সালে রাফেল সেলডন কলকাতার প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হলে কোম্পানির উপর নিজ প্রভাব খাটালেন পঞ্চানন।
সেলডন, পঞ্চাননের দুই পুত্র জয়রাম ও সন্তোষরাম কে বহাল করলেন আমিন পদে। এরপর জরিপ, জমিজমা কেনাবেচা, গৃহ নির্মাণে দালালি করে দুজনেই বেশ পয়সা কামালেন। ধর্মতলা অঞ্চলে নিজস্ব বসতবাড়ি তুললেন জয়রাম।
জয়রামের চার ছেলে মধ্যে নীলমণি 1765 সালে উড়িষ্যায় কালেক্টর হন এবং দর্পনারায়ন কলকাতায় বসেই নানা উপায়ে অর্থ উপার্জন করে ধনী হয়ে উঠলেন। দুই ভাইয়ের মিলে পাথুরিয়াঘাটায় নির্মাণ করলেন বিরাট বসতবাড়ি।
নীলমণি ঠাকুর ও দর্পনারায়ন ঠাকুরের মধ্যে তাদের সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বাধলে নীলমণি ঠাকুর বংশের লক্ষ্মী জনার্দন ও শালগ্রাম শিলা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় এবং পরে কলকাতার মেছুয়া বাজারে অর্থাৎ চিতপুরের কাছে, যা আজকের জোড়াসাঁকো নামে পরিচিত সেই অঞ্চলে এক বিশাল বাড়ি নির্মাণ করেন। সেই বাড়িই পরবর্তীতে ঠাকুরবাড়ি বলে পরিচিত হয়।
নীলমণি ঠাকুর সূচনা করলেও ঠাকুর বাড়ির পুজোয় রাজকীয় জাঁকজমক আসে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই। দ্বারকানাথ নিজেই দেবদ্বিজের ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন পূজা করতেন, হোম করতেন। দুজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত পুজোর ভোগ দেওয়া ও আরতির কাজ করতেন।
দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ ছিলই। ইংরেজ সাহেব -মেমরা যখন বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন, তখন তাদের খাওয়া-দাওয়ার তদারকি দূর থেকে সারলেও তাদের সাথে খাবার গ্রহণ করতেন না তিনি। বরং খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তিনি পোশাক পাল্টে গঙ্গা জল ঢেলে শুদ্ধ হতেন। পরবর্তীতে ব্যবসার খাতির যখন বেড়ে গেল, তখন তিনি আর ছুতমার্গ ধরে রাখতে পারলেন না। ইংরেজদের সঙ্গে খাবার গ্রহণে বসলেন বটে, তবে তিনি তখন থেকে আর মন্দিরে ঢুকতে না। 18 জন ব্রাহ্মণ পুজোর সব দায়িত্ব পালন করতেন। পুজোর সময় তিনি দূর থেকে প্রণাম সারতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মা অলকাসুন্দরী দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা। ইংরেজ ম্লেচ্ছদের সঙ্গে দ্বারকানাথের এই মেলামেশা তার পছন্দ ছিল না, যদিও তিনি ব্যবসার খাতিরে নিয়ম নিষেধে কিছুটা শিথিলতা দেখিয়েছিলেন, কিন্তু দ্বারকানাথের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী ছিলেন এ বিষয়ে শাশুড়ি অলকাসুন্দরীর থেকেও কঠোর। তবে জানা যায় তিনি ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। কথিত আছে দ্বারকানাথের আমলে ঠাকুরবাড়ির দুর্গা প্রতিমার মুখ দিগম্বরী দেবীর মুখের আদলে তৈরি করা হতো। দ্বারকানাথের আমলে দুর্গা পুজোতে রাজকীয় আয়োজন হতো। যে কোন বনেদি বা জমিদার পরিবারের পূজাকে টেক্কা দিতে পারতো ঠাকুরবাড়ির পুজো। পরিবারের সদস্যদের নতুন জামা কাপড় উপহার দেওয়া হতো, ছেলেমেয়েরা পেত দামী দামী পোশাক। যেমন ছেলেদের চাপকান, জরি দেওয়া টুপি, রেশমি রুমাল ইত্যাদি । আসত আতরওয়ালা, জুতোর মাপ নিতে আসত চিনাম্যান, মহিলাদের শাড়ি নিয়ে আসত তাঁতিনীরা। মহিলারা পড়ত নীলাম্বরী, গঙ্গাযমুনা ইত্যাদি শাড়ি।দিনে মহিলারা পড়ত সোনার গহনা আর রাতে জরোয়া। বাড়ির মেয়েরা দ্বারকানাথ ঠাকুর এর কাছে, সুগন্ধির শিশির এবং মাথার সোনার বা রুপোর ফুল উপহার পেতেন আর ছোটরাও পেত শিশি করে আতর। বাড়ির ভৃত্য, কর্মচারী সকলেই পেত নতুন জামা কাপড়।
বিশাল ঠাকুরদালানে হত পুজোর আয়োজন। উল্টো রথের দিন গঙ্গার পাড় থেকে আনা হত প্রতিভা গড়ার মাটি। কাঠামো পুজো হলে তবেই কাঠামোতে মাটির প্রলেপ পড়ত, দিনের পর দিন প্রলেপ চড়িয়ে প্রতিমা তৈরি হতো, কিন্তু সে কাজ হতো সম্পূর্ন পর্দার আড়ালে।
এখানকার প্রতিমার বৈশিষ্ট্য ছিল এক চালা-অর্ধচন্দ্রাকৃতি মূর্তি। পুজোর দিনগুলোতে দিনে দুবার বেনারসি বদলানো হতো দুর্গার। কখনো বেনারসি ছেড়ে দুর্গাকে পড়ানো হতো তসর অথবা গরদ। মাথার মুকুট থেকে কোমরের চন্দ্রহার সমস্ত গহনা পড়ানো হতো সোনার। এমনকি দ্বারকানাথের নির্দেশ অনুযায়ী দশমীর বিসর্জনের সময় সেইসব বহুমূল্যবান গহনা খোলা হতো না।
ঠাকুর বাড়ির দুর্গাপুজোতে ভোগ ছিল দেখবার মতো। অন্নভোগ হত মিষ্টান্ন সহযোগে ৫১ পদের। সঙ্গে থাকত বিভিন্ন ফল ও ডাবের জল। দর্শনার্থীদের মধ্যে পুজো শেষে সেই ভোগ বিতরণ করা হতো। দশমীতে ঠাকুর বিসর্জনের পর ঠাকুরবাড়িতে হত বিজয়া সম্মিলনী। তখনকার বিশিষ্টজনেরা ঠাকুরবাড়ির এই উৎসবে আমন্ত্রণ পেতেন। আমন্ত্রণ পত্র লেখা হতো দ্বারকানাথ ঠাকুরের পিতা রাম ঠাকুরের নামে।
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ঠাকুমা অলকাসুন্দরী দেবীর কাছেই মানুষ, তাই তিনি কখনো কখনো মালা গেঁথে দিতেন শালগ্রাম শিলার জন্য, কালীঘাটে পুজো দিতে যেতেন, নিত্য সূর্য প্রণাম করতেন। কিন্তু যুবক দেবেন্দ্রনাথ যখন রাজা রামমোহনের সান্নিধ্যে এলেন, পৌত্তলিকতা বিরোধী হয়ে উঠলেন, তখন তিনি সংকল্প করলেন, "কোন প্রতিমা কে পূজা করিব না, কোন প্রতিমাকে প্রণাম করিব না, পৌত্তলিক পূজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না"।
1839 সালে দেবেন্দ্রনাথের বয়স বাইশ বছর, সে বছর ঠাকুর বাড়িতে পুজো হলেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুজোর সঙ্গে সমস্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। সে বছর তিনি কখনও পুকুরের ধারে একা বসে এবং তখনও তত্ত্ববোধিনী সভায় একেশ্বরবাদী আলোচনায় সময় কাটালেও পরবর্তীকালে পুজোর সময় তিনি কলকাতা ছেড়ে দেশ পর্যটনে বেড়িয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি ঠাকুরবাড়ির চিরাচরিত পুজো উঠিয়ে দিতে পারেননি।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মাদর্শেই বিশ্বাসী ছিলেন, তার মূর্তি বা প্রতিমা পুজোর প্রতি কোন বিশ্বাস ছিল না কোনোকালেই। তিনি উপনিষদের মনের মানুষের সন্ধান করেছেন সারা জীবনকাল। তবে বাঙ্গালীদের জীবনে, সামাজিকতায়, মানসিকতায় দুর্গোৎসব যে সুখের স্পর্শ, যে আনন্দ ধারা বয়ে এনে দেয় তিনি তাঁর প্রশংসা করেছেন। এই উৎসব যে বাঙ্গালীদের মিলনক্ষেত্র তা তিনি মন থেকেই মেনেছেন। তাইতো লিখেছেন," বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট কিন্তু সমস্ত দেশের লোকে যাতে মনে করে একটা ভাবের আন্দোলন একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয় সে জিনিসটা কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়"।
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পুজো বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে নানান মতভেদ আছে, কেউ বলেন 1857 সালে কেউবা 1858 সালে তো কেউ বলেন 1875 সালে এই পুজো বন্ধ হয়। তবে সত্যিটা হল 1858 সাল থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পুজো চলে যায় শরিকদের হাতে, ক্রমে বন্ধ হয়ে যায় ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো।

লেখিকা পরিচিতি
গার্গী মুখার্জী, রবীন্দ্রমেলার সদস্যা।

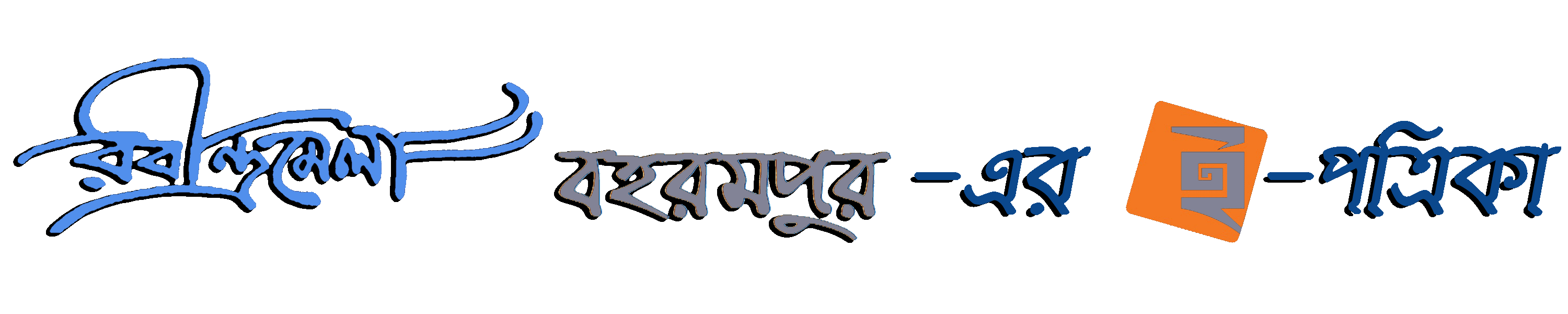
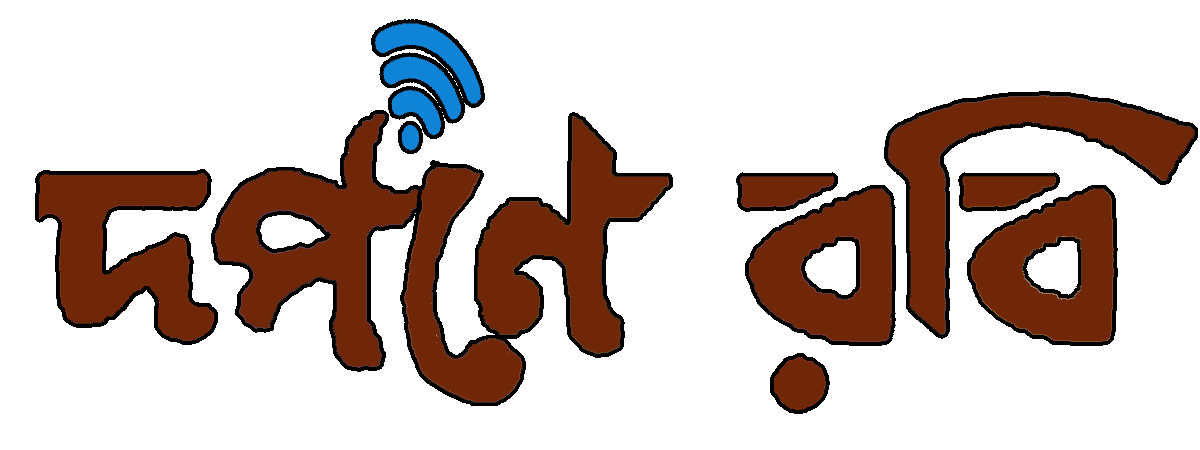



Comments